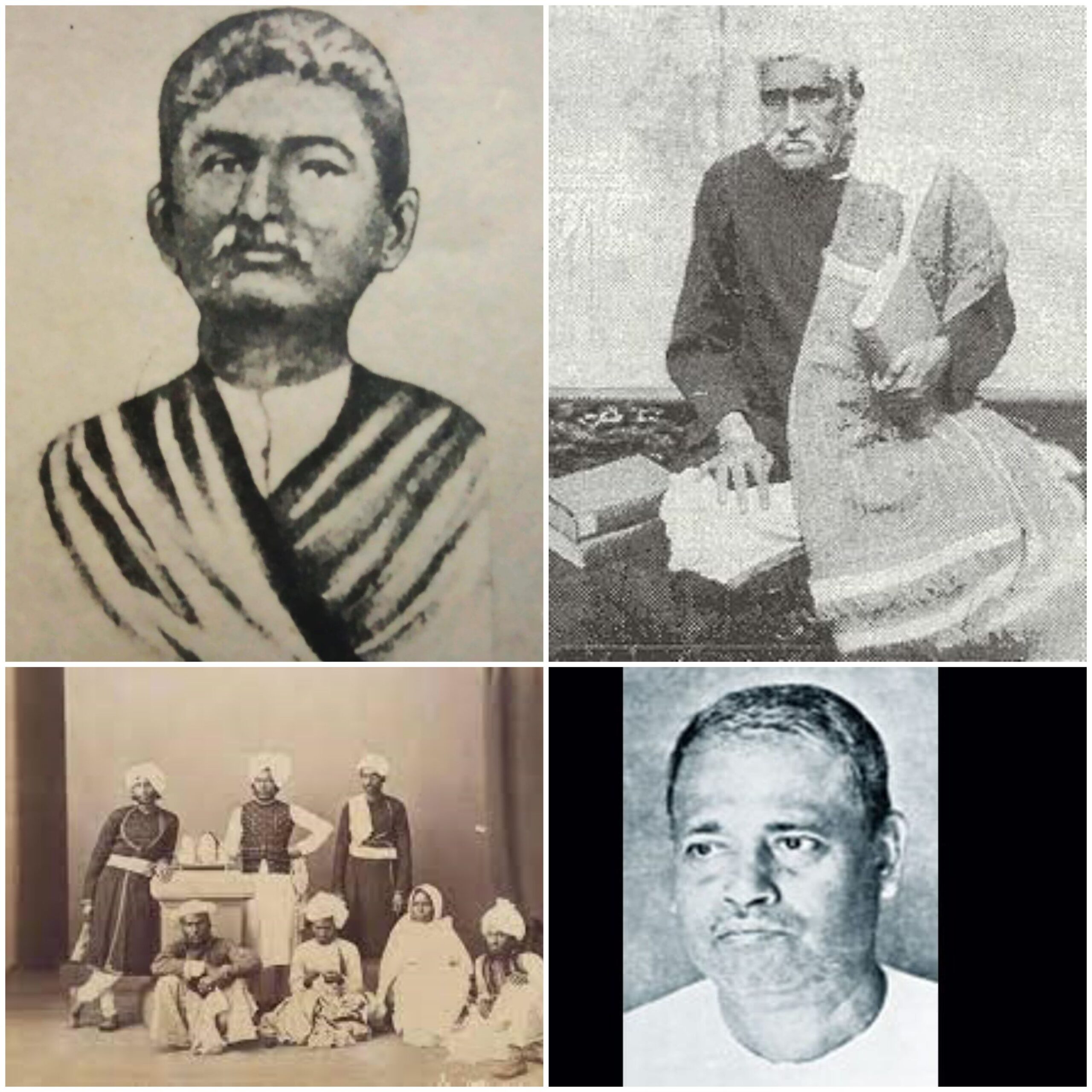ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই ভারতবর্ষের অগ্রগতির দুটি ধারা চলে আসছিলো। এর একটি ছিলো শাসক শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতির সহায়তায় ও তার অনুকরনে স্বদেশের উন্নতি সাধন করা। অপর ধারাটি ছিলো অন্যকারো সাহায্য না নিয়ে অথবা অপরের অনুকরন না করে নিজ চেষ্টায় স্বদেশের কল্যান করা। এই দ্বিতীয় ধারার প্রচেষ্টারই অন্যতম অঙ্গ ছিলো হিন্দুমেলা। নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিঃ কলকাতায় এই হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন বা আয়োজন করেন।
হিন্দুমেলা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় প্রবেশের আগে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন।রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভার আদর্শ ও কাৰ্য্যকলাপ হ’তে “Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal”,
অর্থাৎ, শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিকল্পে একটি সভার অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। এই অনুষ্ঠানপত্র-পাঠে তাঁর অন্যতম বান্ধব নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান।
হিন্দুমেলা-স্থাপনের পর এর অধ্যক্ষতা করবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ-ও তাঁর (রাজনারায়ণ বসুর) সভার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ‘মেলা’ নামটি নবগোপালেরই দেওয়া। মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।
এই চৈত্রমেলায় শিক্ষিত সমাজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা আলোচনা করতে শুরু করেন। এজন্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে এর স্থান স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এর প্রাণ। এ কার্য্যে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাব-বীজটি ফল-পুষ্প- ভারে অবনত একটি সুন্দর মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজী ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে।
প্রথম অধিবেশন:-(১৮৬৭)
জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় বেলগাছিয়াস্থ ডনকিন সাহেবের উদ্যানে সন ১২৭৩ সালের ৩১শে চৈত্র, অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে ১৮৬৭, ১২ই এপ্রিল। প্রথম তিনবছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এ কারণে তখন এটি চৈত্র-মেলা নামে পরিচিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে ‘হিন্দু মেলা’ নামেই এটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। প্রথম বছরে কলকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া উদ্যানে চৈত্র-মেলা স্বল্পাকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । জাতীয় মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্মী মনোমোহন বসু বলেন, “জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিলেন। সে যেন নিজ বাটী ও পাড়াটী বলিয়া শুভকৰ্ম্ম সম্পন্ন করা।” এই বছর রাজনারায়ণ বসু ছুটিতে নিজ গ্রাম বোড়ালে বাস করছিলেন। জাতীয় মেলায় পাঠের নিমিত্ত বোড়াল-বাসীদের রচিত একটি স্বদেশপ্রেমের কবিতা সংশোধন করে তিনি কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেন। এই কবিতাটি তাঁর আত্ম-চরিতে স্থান পেয়েছে।
প্রথমবার অনুষ্ঠানের পর উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন। জাতীয় মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র একযোগে লিখলেন-
“১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।” উদ্দেশ্য গুলি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এ সম্বন্ধে তাঁরা লেখেন-
“১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মুলন্ করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।
২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে। ৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন,
তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে। ৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য
সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।
৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।
৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।”
দ্বিতীয় অধিবেশন:-(১৮৬৮)
দ্বিতীয় অধিবশনে ১৮৬৮ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন:
“এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকৰ্ম্ম-সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ- প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য-ইহা ভারতভূমির জন্য।
ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাজ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়-ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।”
মেলার কার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হ’ল ও প্রত্যেকটি পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক মণ্ডলী গঠিত হ’ল। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বতোমুখী। আর এর সম্পাদনে বঙ্গের গুণি-মানীরা অনেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
হিন্দুমেলার কর্তৃপক্ষগণ জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সজীব করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ঐক্যবোধ-বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য-নানা বিষয়েই এঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করেন। জাতীয় জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কারকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এ সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য, বহু দূরবর্তী হলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় চৈত্র মোলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এ কথা স্পষ্ট ক’রেই ব্যক্ত করেন। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই মেলার কার্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। প্রায় প্রতিবারেই অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ’ত ভারতবাসীর সুবিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ‘গাও ভারতের জয়’। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। ভারতীয় প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচয়িতা।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি।সঙ্গীতের পর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিবরণ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে পাঠ করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পাঠত বিবরণীর একস্থানে তিনি বলেন:
“আবিসিনিয়া যুদ্ধযাত্রাকে ১৭৮৯ শকের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।”
এই সামান্য পঙক্তি কয়টিতে গবর্ণমেন্টের নবানুসৃত সামরিক নীতির ছুটি স্পষ্ট দিক প্রতিভাত। সিপাহীযুদ্ধের পর এমন কোন পল্টন আর রইল না যারা সমুদ্রপারে যেতে আপত্তি করতে পারে। আবার এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের বাইরেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থব্যয় ও ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণ হতে সুরু হয়।
মেলাক্ষেত্রে সংস্কৃত, বাংলা কবিতা, বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং কুস্তি প্রদর্শনের পর উৎকৃষ্ট কুস্তিগীর, লেখক ও শিল্পীদের পারিতোষিক বিতরণ হ’ত। লেখক ও কবিদের মধ্যে পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্ত গুপ্ত। স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশী কুস্তি ও কসরত প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মহিলাদের হস্তনির্মিত সূচীশিল্প-আসন, জুতা, খলে, খরপোস, পশমের ও পৃতীর কার্য্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বারাণসী শাড়ী, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোনার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিত্র ও অন্যান্য ধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনী-বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ দ্রব্য, এবং লাঙ্গল, চরকা, তাঁত প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কুস্তি, অশ্বচালন, পাইকখেলা, বাঁশবাজি প্রভৃতি খেলা দেখানো হ’ত।
চৈত্রমেলায় একজন হতেন সভাপতি। তবে সভাপতিকেই যে প্রধান বক্তা হ’তে হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বৎসরে মেলার সভাপতি হন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিন্তু প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু মহাশয়। ইনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। হিন্দু-মেলার আদর্শে মফস্বলেও বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বাংলা ১২৭৬ সাল থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হ’তে থাকে। এ মেলার তৃতীয় অধিবেশনে ১২৭৮, ৩০শে ফাল্গুন মনোমোহন বসু প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেলা হয় কলকাতার পাশি বাগান উদ্যানে। ১৮৭৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রাজনারায়ণ সভাপতি-রূপে বরোদানিবাসী বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সকে সঙ্গীত ও নড়ালের জমিদার রাইচরণ রায়ের ব্যাঘ্রশিকারে নৈপুণ্য-প্রদর্শন জন্য স্বর্ণপদক উপহার দেন। এবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন মাত্র চতুৰ্দ্দশবর্ষীয় বালক) ‘হিন্দুমেলার উপহার’ নামে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর-একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন তাঁকে উদ্দেশ ক’রেই এ কবিতাটি লিখিত। এর প্রথম কয়েক পঙক্তি এরকম-
“দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?”
মেলা এর পরও কয়েক বৎসর চলেছিল। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত যে এর রীতিমত অধিবেশন হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।
যে ব্যাপক আদর্শ নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ চৈত্রমেলা উদ্যাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা স্বদেশপ্রেমিক মনোমোহন বসুর বক্তৃতাসমূহে। মনোমোহন সে-যুগের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি।
তিনি ‘মধ্যস্থ’ নামে একখানা পত্রিকারও (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক) সম্পাদনা করেছিলেন। বাঙালী তাঁরই কাছে জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষা নিলে। তাঁর নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়। তিনি দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণের
প্রথমেই বললেন:
“স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐকানামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস নয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ ‘স্বাবলম্বন’ নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন-সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এ সমাবেশ-রূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য-স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।”
চৈত্রমেলা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই মিলনভূমি। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন:
“ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্তক। অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।”
তিনি তাই স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করে বলেন:
“অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যৈষ্ঠ সংস্কৃত তাঁধার জন্য, শারীরিক বলাধান জনা, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্প-বিজ্ঞান জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই। আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়। অনাদর করা নির্ব্ব স্কির কর্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে। যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে-যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলায় প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল। সেই শুভ ফল না আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক-ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই। জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন। চেষ্টা করিলে কখন ব্যর্থ হইবে না।”
তৃতীয় অধিবেশন:- (১৮৬৯)
জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন হয় বেলগাছিয়াস্থ ডনকিন সাহেবের উদ্যানে পরের বছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে। আগের বছরের কর্মপদ্ধতিই অনুসৃত হয়। এবারেও প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু। সভাপতি হয়েছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়। এবারের প্রদর্শনীটিকে আরও বেশি সুষ্ঠুভাবে করবার চেষ্টা করা হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারু ও চারু শিল্প প্রদর্শিত হয়-
শিল্প-(১) স্ত্রীলোকদের সূচি নির্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য,
(২) ছাঁচ ও খয়েরের গঠন,
(৩) জামা, চাপকান, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়নী, সাটী ইত্যাদি,
(৪) কুম্ভকারদিগের নির্মিত নানাবিধ ফল,
(৫) নদিয়ার বাজার,
(৬) নানাপ্রকার পুতুল,
(৭) চিত্র,
(৮) বারাণসী কাপড়,
(৯) চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়,
(১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানাপ্রকার রূপা ও সোনার গঠন,
(১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র,
(১২) নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র,
(১৩) ফোয়ারা,
(১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্তি। উদ্ভিজ্জাদি-ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ; কৃষি ও শিল্পকারক যন্ত্রাদি-লাঙ্গল, চড়কা ও তাঁত।
এছাড়াও এই সকল ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শিত হয়:
রাসায়নিক ক্রিয়া, কুস্তী, অশ্বচালন, পাইকের খেলা ও বাঁশবাজী।
শিল্পকর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাদের ‘হিন্দু মেলা’ নামাঙ্কিত এক একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয়-
“মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন (প্রসাদ?) গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বসুর পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্রের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন মল্লিকের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু হরিবল্লভ ‘বসুর পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার
শ্রীমতী সতী দেবী,কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।”
এবারেও সাহিত্য-বিভাগে কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত এ বৎসর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে কলিকাতার শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ও বাহির সিমুলিয়া ব্যায়াম-বিদ্যালয় থেকে ব্যায়ামকুশলীরা কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক লাভ করেন।
হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু মহাশয় সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ ‘জাতীয়তা-বোধ’ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:
“সামাজিকতার যে অন্ত একটি মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য। তাহাকে পাইবার জন্তই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না-সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছ, ঙ্খলার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধৰ্ম্ম। সেই স্বজাতিধৰ্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্বপ্রযত্নে বিধেয়।”
কিন্তু তা করতে গেলে আগে ‘আত্মনির্ভর’ নামক শাণিত অস্ত্র দ্বারা ‘পরবশ্যতা’ রূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করতে হবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করবার জন্য এইরূপ সমাবেশই অদ্বিতীয় উপায়। তাই মনোমোহন বলেন:
“স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব-বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কিবা উন্নতি আর কিবা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনাপূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কাৰ্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।”
কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করলেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। মনোমোহন বসু মহাশয় অভিভাষণে তাই স্বদেশসেবার বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ ক’রে বলেন:
“[অর্থসাহায্য ব্যতীত। যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্য ব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্তব্য। যিনি বিদ্বান, তিনি অধ্যক্ষ শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাবসূত্রে গ্রন্থ করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীতরসে মেলাভূমিকে অমৃতরসে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতি যোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য, এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন।”
চতুর্থ অধিবেশন :-(১৮৭০)
চতুর্থ অধিবেশন থেকে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে-এই বছর থেকে সাধারণতঃ মাঘ-সংক্রান্তি ও পরবর্তী দিনে মেলা হতে থাকে।’ এই বছর থেকে মেলার কোন মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায়নি। সমসাময়িক সংবাদপত্রে যতটুকু বিবরণ প্রকাশিত হয় তাই বর্তমানে একমাত্র সম্বল।
মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়-
“হিন্দু মেলা। বিগত শনিবার (১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি) মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়াস্থ প্রশস্ত উদ্যানে মহাসমারোহে হিন্দু মেলা নির্বাহিত হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে উক্ত দুই দিবসই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক একত্রিত হইয়াছিল। তথায় এতদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষগণের কৃত শিল্পাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষিপ্রদর্শন এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদির পরিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল দ্রব্যাদির প্রদর্শন হয় তাহা অতি চমৎকার, সকলে সেই সকল দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছেন। আমরাও এতদ্দেশীয়দিগের প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্রাদি এবং পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয়দিগের সংগীত ও শিল্প শাস্ত্রাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বর্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য সমালোচন করতঃ দুঃখিত হইয়াছি। মেলার কার্য্যবিবরণ পাঠ, এতদ্দেশীয়দিগের উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীষ্মদেবের জীবনচরিত ঘটিত পুরস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্দুস্থানী বক্তৃতা প্রভৃতি যে সকল সভার কার্য্য দেখা গেল তাহাতে বোধ হয় এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, নৌকার বাচ্, অশ্বচালন প্রভৃতি বিষয়ে অপূর্ব্ব কৌশল সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমোদজনক নানা প্রকার সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী, সাধারণের হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। একদল ঐকতান বাদক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা যেরূপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার কোন অংশই নিন্দনীয় নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণেরই এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা কর্তব্য। অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই-এই মেলার প্রারম্ভে ইহার
নাম চৈত্র মেলা রাখা হয়। কিন্তু সাধারণে চৈত্রমাসে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সময় পরিবর্তনের অনুরোধ করাতে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া হিন্দু মেলা নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম এবারেও দুই জনের ‘সদীগর্মী’ হইয়াছিল। বিশেষ এ সময়েও রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র মেলার নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তখন আরও একমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ মাঘ মাসে হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।”
চতুর্থ অধিবেশন সম্পর্কে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ দিবসীয় ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ এইরূপ লেখেন-“জাতীয় মেলা। সমাজের বর্তমান অবস্থা ইহার পরিণাম নহে। ইহা সহস্র ২ বার বিয়োজিত, গঠিত, পরিবর্তিত হইলে, যদি কস্মিনকালে ইহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা যত আলেচিত বিলোচিত হয়, তত মঙ্গল এবং এই নিমিত্ত যেখানে যখন যে কোন রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই প্রায় শুভকর ফল দেখা গিয়াছে।
“আমাদের সমাজ অনেক অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় শাসন সহ্য করিয়াছে এবং তাহাতে ইহাকে একরূপ নির্জীব ও নিস্তেজ করিয়া তুলিয়াছে। একটু নাড়াচাড়া না করিলে আবার উহার চৈতন্য জীবন্ত হওয়ার সম্ভব নাই…।
“জাতীয় মেলাটি এইরূপে আমাদের সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নতির অভিমুখ লইতেছে কিন্তু ইহার উদ্দেশ্যও মহৎ, সুতরাং ইহাতে যত কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আমরা তত বিশেষ উপকৃত হইব।
“এ বৎসর চৈত্র মাসে না হইয়া ফাল্গুন মাসে হওয়ায় মেলায় উপস্থিত সকলে গ্রীষ্ম কর্তৃক তত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও এবার আয়োজনের কতক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।…
“মেলাতে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রদর্শনী হয়। কথকতা, রাসায়নিক প্রদর্শন, লিখিত বক্তৃতা পাঠ, গান, কৃত্রিম ফল, ফুল, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি উপযোগী যন্ত্রের প্রদর্শন, বাংলা পুস্তক, তদ্ভিন্ন ফল, ফুল, চারুকার্য্য এবং শেষ দিন কুস্তি লাঠিখেলা, নৌকার বাজী প্রভৃতি হয়।”
দ্বিজেন্দ্রনাথ যেমন মেলায় স্বদেশীয় চিত্র প্রদর্শনের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন, ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ তেমনি ইহাকে স্বদেশীয়দের বলবীর্য্যের প্রকাশক্ষেত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। মেলায় প্রদর্শিত বিষয়াদির সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকা লেখেন-
“উপরের তালিকাটি দেখিলেই সহসা বোধ হয় এটি ক্রমে ইংরাজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফিয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।”
মেলা সম্পর্কে পত্রিকার পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য-
“আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা বোধ করি কৃষ্ণকামিনীর চারু কার্য্যের পারিপাট্যতার কথা শুনা অপেক্ষা অনেকে ‘মেলায় ঘোড় দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠি খেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুড়াতে একজন মরিয়াছে’ শুনিয়া অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইতেন।”
পঞ্চম অধিবেশন :-(১৮৭১)
এর পর মেলার পঞ্চম অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের স্বাক্ষর বিজ্ঞপ্তি যথারীতি প্রচারিত হয়। নতুন গ্রন্থ, উত্তম শিল্প, কৃষিদ্রব্য, বাজার, দোকানদার, গীতবাদ্য, খেলা, নিলাম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের বিষয় নির্ব্বাচনের ভার বিভিন্ন ব্যক্তি বা মণ্ডলীর উপর অর্পিত হয়। বিজ্ঞাপনটির ‘নতুন গ্রন্থ’ অনুচ্ছেদে লেখা হয়-
“যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রকার উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ মেলার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে ন্যাশনেল প্রেসে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে যদি তৎসমুদয় মেলার অধ্যক্ষ সভার বিবেচনায় নূতন ভাবাত্মক ও দেশের যথার্থ হিতজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মেলার সময় বিশেষ সম্মানসূচক চিহ্ন ও সাধ্যমতে অন্য প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে, যাঁহারা উক্ত প্রকারের কোন গ্রন্থ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পাণ্ডুলিপি যদি উক্ত সভার মনঃপূত হয় তবে তাঁহাদিগকে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাধ্যমতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে।”
‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ (২০ শে জানুয়ারি, ১৮৭১) বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করে লেখেন-
“অন্য স্তম্ভে পাঠক চৈত্র মেলা, এখন মাঘ মেলা, সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন দেখিবেন। আমরা এই বিজ্ঞাপনটির নিমিত্ত তিন স্তম্ভ পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে পাঠক বুঝিবেন যে এ বিষয়টিকে আমরা কত গুরুতর মনে করি। এ মেলাটি শুধু কলিকাতাবাসীদিগের নিমিত্ত নহে, সমস্ত বাঙ্গালার জন্যেই। আমরা ভরসা করি দূর দেশ হইতে ভদ্রলোক মেলা দেখিতে যাইবেন, যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মেলার কর্তৃপক্ষীয়দিগকে আমরা আর বৎসর যাহা বলিয়াছিলাম এ বৎসর সে অনুরোধ করি। তাঁহারা যেন মানসিক উন্নতিকে আনুষঙ্গিক করিয়া শারীরিক উন্নতিকে প্রধান সংকল্প করেন।”
এ বছর জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন (১১, ১২, ১৩ই ফেব্রুয়ারি) কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ দূরে হীরালাল শীলের বাগানে।
এই অধিবেশনে মনোমোহন ধনী ও ভূস্বামীদের ঔদাসীন্যের জন্য খেদ প্রকাশ ক’রে বলেন, “রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা এবং সাধারণ ঐক্যবিধান বিষয়ে এই হিন্দুমেলা, আমাদিগের মগ্নাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ হইয়াছে; এই দুইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক, ভগবানের কৃপা হইলে এই উভয়ের সাহায্যেই অকূলে কূল পাইতে পারি।”
রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান বা ভারতবর্ষীয় সভা মুখ্যতঃ একটি জমিদার-সভা হইলে তখনও স্বদেশবাসীদের মুখপাত্র-রূপে কর্মে লিপ্ত ছিল। এ সভায় বাংলার ধনী মানী ভূম্যধিকারীরাই অধিক সংখ্যায় সমবেত হতেন। সাধারণ শিক্ষিতেরা অধিক সংখ্যায় এর আওতার ভিতরে যেতে পারতেন না। এজন্য সভার কর্মগুলিতে তাঁদের মতামত কমই গ্রাহ্য হ’ত। সপ্তম দশকের প্রারম্ভেই এ সভার বিরুদ্ধে তাই তখন নানারূপ প্রতিক্রিয়া হতে সুরু হয়। একথা পরে বলব। কিন্তু মনোমোহন বসু মহাশয় হিন্দুমেলার পক্ষ থেকে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন অর্থ সাহায্য দ্বারা এর সুফলপ্রস্থ কার্যকলাপকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁদের লক্ষ্য ক’রে ভাষণটিতে বলেন:
“আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয় রে আমার ধন-কুবের প্রধান সন্তানগণ! আয় রে রাজ্যাধিকারি-ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তিনি অচিরে নির্মল আনন্দমন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশাভরসা-মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ সম্পত্তি, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে? তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে-যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; করিও না; জাগরূক হও, উত্থান কর, জননীর দুঃখাবমার্জনে আর বিলম্ব চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর, আশারূপ গাছ তোমার করতলে লও, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কৰ্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও-চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে-শ্রবণ কর, স্বজাতি-কুঞ্জের গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয়-জয়ন্তী তানে গান করিতেছে-নববঙ্গের নবোদ্যম কুসুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে-নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষা-রূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকরশ্রেণীরূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে-আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর ‘সৌভাগ্য অরুণ’ তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর, সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোক-বাসী সকলই শব্দ করুক ‘জয় জয় জয়!’ হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, ‘জয় জয় জয়!’ আকাশে শব্দ হউক ‘জয় জয় জয়!’
‘হিন্দু মেলার জয়!’ ‘হিন্দু মেলার জয়!’ ‘হিন্দু মেলার জয়!’
হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। ‘পরবশ্যতা’ দূর ক’রে স্বাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করতে পারলে আমরা স্বজাতিধৰ্ম্ম ফিরে পাব। তখন আমাদের মূল লক্ষ্য আসবে হাতের মুঠোর মধ্যে। বারুইপুরে অনুষ্ঠিত মেলায় মনোমোহন আমাদের আদর্শের নাম দিয়েছেন ‘উন্নতি’। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ তাঁর শ্রোতা। সুতরাং একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এর মর্মকথা তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: “শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা! তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্রআছে; প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যান-তত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য! উদ্যম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্রদ্বারা দৈত্যপতি ‘পরবশ্যতার’ বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন!”
ষষ্ঠ অধিবেশন:-( ১৮৭২)
মেলার অধিবেশনের কিছুকাল আগে থেকে বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। জাতীয় মেলার এই অধিবেশন হয় মৃত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরস্থ বিখ্যাত বাগানবাটীতে যথারীতি মাঘ-সংক্রান্তি ও ১লা ও ২রা ফাল্গুন দিবসে (১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি)। শেষ দিন বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলে মেলার অধিবেশন এবারকার মত বন্ধ হয়া যায়।
একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মেলার প্রথম থেকেই সাহিত্য, শিল্প ও ব্যায়াম এই তিনটি জিনিষের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কারণ জাতীয় উন্নতি বলতে এই তিনটির উৎকর্ষ ছাড়া আর কি হতে পারে? এই অধিবেশনে চারুশিল্প বিভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য একটি সুবর্ণ পদক এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলো-ছায়াময় চিত্রের জন্য আর একটি রৌপ্যপদক দানের ব্যবস্থা হয়।
কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য তিনশ টাকা পরিমাণ পুরস্কারের বরাদ্দ ছিল। মল্ল, কুস্তি-কসরৎ প্রদর্শক ও ব্যায়ামবীরদের জন্যও যথারীতি পারিতোষিকের বরাদ্দ হয়। জাতীয় মেলায় এবারে উৎকৃষ্ট পুস্তক-লেখক ও প্রবন্ধকারদের পুরস্কার দানের পরিবর্তে এখানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় তা এবং এ বিষয়ে প্রাপ্ত অন্য টাকা-কড়ি ‘হিন্দু-প্রদর্শক’ পত্রিকার প্রচারের জয ব্যয় করা জাতীয় সভার সাহিত্য-বিভাগ ধার্য্য করেছিলেন। তবে মেলার অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ যথারীতি হয়েছিল। এই অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি থেকল জানা যায়, জাতীয় মেলার সাধারণ সভার অধিবেশন বছরে দুই বার হওয়া স্থির হয়। এরপর বিবেচনার জন্য কর্মকর্তৃসভার কার্যাবলী ঐ ঐ সময় উপস্থাপিত করার কথা থাকে। কার্য্য-পরিচালনার নিয়মাবলী ধার্য্য করার ক্ষমতাও সাধারণ সভার। সাধারণ সভার সভ্য ছিলেন-বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিজয়কেশব রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ ছিলেন-কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।’
সপ্তম অধিবেশন:-( ১৮৭৩)
জাতীয় মেলার আয়োজন যথারীতি আরম্ভ হল। ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের দিন ধার্য্য হল। এবারে অধিবেশন হইল হীরালাল শীলের নৈনানস্থ বাগানে। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে লিখলেন-
“জাতীয় মেলা। ফাল্গুন মাসের এই তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশ হইবে।… স্রোতের গতি ফিরিয়াছে, এখন হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায় তাহার প্রতি অনেকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব যখন পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গের কত যে উৎসাহ হয়, তাহা বলা যায় না।…
“বাবু নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যায়ামচর্চ্চার নিমিত্ত স্কুল খুলিয়াছেন এখন তাঁহার এই মাত্র যত্ন যে, ইহার কিসে শ্রীবৃদ্ধি হয়। ক্যাম্বেল সাহেব আর যত অনিষ্ট করুন, তিনি আমাদিগকে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষায় উৎসাহ দিয়া বিশেষ উপকার করিতেছেন।…
অধিবেশন আরম্ভ হল। প্রথম দিন মেলায় যাঁরা চাদা দান করেছিলেন এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মেলা-ক্ষেত্রে সভা হল। তার পৌরোহিত্য করেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁর প্রারম্ভিক অভিভাষণের পর অন্যতর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত বৎসরের কার্যকলাপ সম্পৃক্ত একটি বিবরণ পাঠ করেন। তিনি এতে জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। হিন্দুজাতির পূর্ব্বগৌরব ও বর্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা পূর্ব্বক তিনি জাতীয় উন্নতিবিধান কল্পে সকলকে অবহিত হতে অনুরোধ করিয়া বিবরণ শেষ করলেন। মেলা উপলক্ষে রচিত কয়েকটি স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীত বাজনা সহযোগে গাওয়া হবার পর এদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।
অষ্টম অধিবেশন, ১৮৭৪
হিন্দু মেলার অষ্টম অধিবেশন হয় কলকাতার পার্শীবাগানে ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী। জাতীয় মেলার অধিবেশন এই প্রথমবার কলকাতা নগরীর মধ্যে হয়। এই কয় দিনের উৎসবের বিবরণ ‘মধ্যস্থ’ সংক্ষেপে দিয়েছেন। প্রথমেই ‘মধ্যস্থ’ লেখেন-
“এ বৎসর মাঘ-সংক্রান্তি বুধবার দিবসে মেলার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য বারে নগরের বাহিরে কোন দূরস্থ উদ্যানে মেলা হইত, এবারে শহরের মধ্যে মৃর্জাপুরস্থ বিখ্যাত পার্শীবাগানে তাহা হওয়াতে সাধারণের পক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু আট আনা হারে প্রবেশ-টিকেটক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় তত লোক হয় নাই। তথাপি সহস্র সহস্র মহাশয়েরা যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরম ভাগ্য…।”
প্রথম দিনের দুপুরে মেলাক্ষেত্রেই জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হল। তাতে পরবর্তী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিতরূপে অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত কর্মচারীসমূহ মনোনীত হন। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি; বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত, এম.এ. সম্পাদক; বাবু ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তথা বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।
“শুক্রবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য মেলার উদ্যানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজনারায়ণ বাবু ও প্রাণনাথ বাবু উৎসাহসূচক কিঞ্চিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত পারিতাষিক দান বিষয়ে বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন।
“শনিবার দিবসীয় মেলায় নবগোপাল বাবু গত বৎসরের প্রধান প্রধান সামাজিক ঘটনা বিবৃত করেন। এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্তৃক “বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তৎপরে রাজনারায়ণ বসু মেলার সংক্ষিপ্ত ‘ইতিহাস ঘটিত একটি বক্তৃতা করেন।
“রবিবার যে বৃহতী সভা হয়, তাহাতে রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রধান আসন গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে তাঁহার পরিবর্তে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য নির্বাহ করিলেন। বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্তৃক সংক্ষেপে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির বিবরণ লিপির পাঠ হইল।
“মন্তব্য লিপি পাঠ সমাপ্ত করা হইলে বাবু মনোমোহন বসু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।… তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেলার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের আশা ও উৎসাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন…।
“রবিবারে যা যা প্রদর্শিত হয় তাহার তালিকা হল-
১। ক্ষেত্রজ বহুবিধ ধান্য তণ্ডুলাদি শস্য এবং উদ্যানজাত নানারূপ ফলমূল শাকসব্জি
লতা গুল্ম ইত্যাদি।
২। শিল্প।
৩। জন্তু প্রদর্শন।
৪। নাটক। জাতীয় নাট্যশালার নটগণ অভিনেতা; এজন্য এক টাকা হারে স্বতন্ত্র
টিকিট।
৫। ব্যায়াম। এক্ষেত্রেও আট আনা হারে স্বতন্ত্র টিকিট হয়েছিল।
৬। কুস্তি।
৭। বেদের ভেল্কি, সাপ-খেলানো, ভালুক লড়াই প্রভৃতি তামাসা।
৮। কুমারের চাক, তাঁতির তাঁত প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের পরিচালন।
১। আতশবাজী। প্রদর্শকগণকে যথোচিত পারিতোষিক দেওয়া হয়েছিল।
নবম অধিবেশন:-(১৮৭৫)
জাতীয় মেলার বাৎসরিক অধিবেশনের সময় যতই নিকটবর্তী হতে থাকে ততই নবগোপাল মিত্র আহারনিদ্রা ত্যাগ করে তার আয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর করতে উঠে পড়ে লাগেন।
‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ (৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) ইংরেজী স্তম্ভে লিখিলেন, “Babu Nobogopal has left off eating, sleeping and is roaming from door to door.” এ বৎসর পার্শীবাগানে মেলার অনুষ্ঠান হইল, এবং পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ইহার অধিবেশন চলিল। এবারে সভাপতি হইলেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। ‘সোমপ্রকাশ’ (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) প্রথমেই লেখেন-“হিন্দু মেলা। …৩০ শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার) ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজ (৪ঠা ফাল্গুন) শেষ হইবে। এ মেলাটি বাবু নবগোপাল মিত্রের দৃঢ়তর যত্নের ফল। ইহা আজিও যে নির্ব্বাণ হয় নাই, নবগোপাল বাবুর অস্খলিত অধ্যবসায়ই তাহার কারণ। ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। আমরা প্রথম প্রথম ইহার ধরণ দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের হরিদ্বার ও হরিহরছত্র ও বারুণী প্রভৃতি মেলার ন্যায় এটিও একটি উৎসব ক্ষেত্র হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহা ক্রমে আমোদ-ক্ষেত্র না হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের দেশের বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলাস্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কি উপায়ে দেশের কৃষি-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুরা একবাক্য হইয়া স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, এই চেষ্টা হইতেছে। এগুলি অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।…”
দশম অধিবেশন:- (১৮৭৬)
জাতীয় মেলার নবম ও দশম অধিবেশনের মধ্যবর্তী এক বৎসর বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। আনন্দমোহন বসুর স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বা ছাত্রসভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নব্য ইটালী, ম্যাটসিনি, শিখশক্তির অভ্যুদয় প্রভৃতি শীর্ষক যে-সব বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তাতে বঙ্গের যুবক-সমাজ একেবারে যেন মাতে উঠেছিল।
শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ সাধারণ শিক্ষিতের অধিগম্য একটি রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠায়ও তৎপর হয়েছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ‘ইণ্ডিয়ান লীগ’ নামে একটি সর্ব্বসাধারণের রাজনৈতিক সভা গঠিত হয়। জাতীয় মেলা যে-সব উদ্দেশ্য সাধনে এতদিন তৎপর ছিলেন তাহাও এই সভার কর্তব্য মধ্যে গণ্য হয়। এর প্রধান অনুষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রও এই সভার কর্মকর্তৃসভায় স্থানলাভ করেন। জাতীয় মেলা একাকী যে-সব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়েছিলেন।
এতদিনে সাহিত্য, নাটক, কাব্য, পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ এবং ইণ্ডিয়ান লীগের মত রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়ে তা বস্তুগত হবার অবকাশ পেল। এর পরও জাতীয় মেলার বার্ষিক অধিবেশন হতে লাগল। জাতীয় মেলার দশম অধিবেশন হল ১৮৭৬ সালের ১৯ শে ও ২০ শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনচাঁদের টালা-উদ্যানে।
এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ‘সোমপ্রকাশ’ (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) বলেন, “এ বৎসর হিন্দু মেলায় আন্দুল নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি অক্ষর নির্মাণের ও কাগজ প্রস্তুত করিবার কল প্রদর্শন করেন।”
পরবর্তী অধিবেশন সমূহ:-
জাতীয় মেলার একাদশ অধিবেশনেও পূর্বের ল রীতি অনুসৃত হয়েছিল। এবারকার অধিবেশন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নি বলে দুঃখ করে ‘সাধারণী’তে (৪ মার্চ ১৮৭৭) এক ব্যক্তি লেখেন-
“দেখিবার মধ্যে একটি কাপড়ের কল, দেশীয় দেশলাই (match box) কালি, এবং সাবান দেখিলাম।…কি করিয়া ‘মিরার’ সম্পাদক মেলার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন জানি না,….।”
দ্বাদশ অধিবেশন (১৮৭৮) হইতে জাতীয় মেলা মাঘ-সংক্রান্তির পরিবর্তে সরস্বতী পূজার সময় অনুষ্ঠিত হয়।
১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ অধিবেশন।
চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। চতুৰ্দ্দশ অধিবেশন সম্পর্কে ‘সুলভ সমাচার’ (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০) দুঃখ করিয়া লেখেন-
“২৯ শে মাঘ হইতে রাজাবাজার ব্রজনাথ ধরের বাগানে হিন্দুমেলা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার উন্নতি না হইয়া দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।”
হিন্দুমেলা শিক্ষিত সাধারণের মনে যে নবজাতীয়তার উন্মেষ সাধন করেছিল তা আমরা পরবর্তী সময়ের ঘটনাপরস্পরায় সম্যক উপলব্ধি করতে পারব। এই সময়ে বহু মনীষী হিন্দুমেলার নবজাতীয়তার সূত্র গ্রহণ ক’রে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হ’তে অহর্নিশ উপদেশ । কারণ আত্মনির্ভর না হ’লে আত্মশক্তি অর্জন অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে এই আত্মশক্তিই যে সবচেয়ে বড় কথা।
তথ্য সহায়ক গ্রন্থ –
১) মুক্তির সন্ধানে ভারত, শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল। অশোক পুস্তালয়, ৬৪ মহাত্মাগান্ধী রোড,কলিকাতা -৯
২)হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত,শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়,সংকলক অশোক উপাধ্যায়। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।
৩)বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৬
৪) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ ৩৫
৫) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ, ২য় সংস্করণ, পৃ ২৫৭
৬) The National Paper, Feb-14&21,1872
৭) রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ১৩১৫, পৃ. ১২৯-১৩০।
৮) মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, হিন্দুমেলার কার্যবিবরণ, ১৭৯০ শক।
(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)