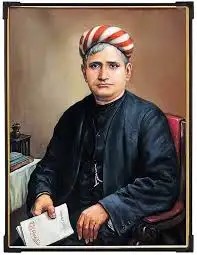সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা তীব্র আক্রমণ ও বিতর্ক
তার জীবদ্দশায় যেমন হয়েছে তার মৃত্যুর পরবর্তীকালেও সেই ধারা অব্যাহত
থেকেছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক সারা বিশ্বজুড়ে অগণিত। ঈদের মধ্যে বঙ্কিম
অনুরাগী যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে বিরুদ্ধবাদী! এই বিরুদ্ধবাদীরা সাহিত্য
সম্রাটের সমালোচনা বরং বলা ভালো নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে
গভীরভাবে পাঠ করেছেন। বঙ্কিমের এই সমালোচকের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় লেখকই
ছিলেন। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশের পর সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণ উপন্যাসটির বিভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করলেও বইটির তীব্র সমালোচনা
করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন দুর্গেশনন্দিনীর ত্রুটি
প্রদর্শনে তৎপর হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের
পরও সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, হালিশহর পত্রিকা, জাতীয় পত্র-পত্রিকায়
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আক্রমণ করার কথা।
১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন সাধারণ মানের লেখকও
‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকে উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে যে চরিত্রটি সৃষ্টি
করেছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্যারিকেচার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমনকী
বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন নবীনচন্দ্র সেনও নৈতিকতার প্রশ্নে
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ১
একই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন কয়েকজন মুসলমান লেখক।
তাঁরা উপন্যাসের সাহিত্যিক গুণাগুণ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট মুসলিম চরিত্র
সম্পর্কে সুতীব্র আক্রমণ করেছিলেন। এই প্রবণতা পরবর্তীকালেও কোনো কোনো মহলে
প্রচলিত ছিল; যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছে
যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠক-লেখক মাত্রেই বঙ্কিম-বিরোধী এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম
ধর্মাবলম্বীদের কাছে ‘মুসলিম বিদ্বেষী’ বলে পরিচিত।
বঙ্কিম-বিদ্বেষের সূচনা:-
উপন্যাস রচনার শুরু থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বিতর্কিত লেখক। ‘দুর্গেশনন্দিনী’
প্রকাশের (১৮৬৫ খ্রিঃ) সময় থেকেই হিন্দু সমাজপতিরা তাঁর ওপর খড়গহস্ত। অভিযোগ
উঠল যে, তিনি নাকি শিল্পসৃষ্টির নামে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও পরিবারকে ধ্বংসের
মুখে ঠেলে, দিচ্ছেন। তাঁর উপন্যাস পাঠ করে হিন্দু বিধবারা প্রেম-প্রণয়ে
অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, এবং সধবারা পূর্বপ্রণয়ীদের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসাহ
পাচ্ছেন-হিন্দু নর-নারী অবৈধ জীবন যাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। অপর একটি দল অবশ্য
তাঁকে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য অভিনন্দনও জানাচ্ছেন।
কিছুদিন পর হিন্দু সমাজের ক্ষোভ যখন মোটামুটি স্তিমিত, ঠিক এ সময়েই প্রকাশিত
হল তাঁর তিনটি উপন্যাস-‘রাজসিংহ’ (১৮৮২ খ্রিঃ) ‘আনন্দ মঠ’ (১৮৮২ খ্রিঃ) এবং
‘সীতারাম’ (১৮৮৭ খ্রিঃ)। এবার মুসলিম সমাজ তাঁর প্রতি খড়গহস্ত হল। বলা হল যে,
ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নামে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম শাসক শ্রেণি, তথা সমগ্র
মুসলিম সম্প্রদায়কে হেয় করতে তৎপর।
‘দুর্গেশনন্দিনী’ ‘বিষবৃক্ষ’ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য
হিন্দুদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, ঠিক
অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল মুসলিম সমাজের মধ্যে তাঁর ‘চন্দ্রশেখর’,
‘রাজসিংহ’, ‘আনন্দ মঠ’, ‘সীতারাম’ প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য। মজার কথা হল এই যে,
মুসলিম সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ক্ষুব্ধ দেখে, হিন্দু সমাজপতিরা
যাঁরা তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের
পাশে দাঁড়ালেন। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণাই দৃঢ় হল যে,
বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম-চরিত্রগুলিকে হেয় করার জন্যই উপন্যাসগুলি
রচনা করেছেন।
এর ফল হল মারাত্মক। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম-বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত
হলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হল বিপুল পরিমাণ হীন সমালোচনা – সাহিত্য,
আক্রান্ত হল হিন্দু সমাজ। এর ফল-স্বরূপ হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা বৃদ্ধি পেল।
জনৈক আহমদ মিঞা লিখছেন-“এই বঙ্গদেশে যদি বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র ও হরিসাধন
প্রভৃতি মুসলমানের কুৎসা কাহিনীতে পরিপূর্ণ নাটক ইত্যাদি প্রচারিত না হতো
তাহলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান এত বিচ্ছেদ-ব্যবধানে পতিত হতো না।”২ ঠিক এ ধরনের
মন্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। তিনি ‘ঐতিহাসিক
চিত্রোদ্ধার’ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি
মুসলিমদের কলঙ্ক অঙ্কনে মনোযোগী না হয়ে তাঁদেরকে প্রেমপাশে বাঁধতে সচেষ্ট
হতেন, তাহলে মুসলিম সমাজ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হতো না। এর ফলে হিন্দু লেখকদের
অঙ্কিত মুসলিমদের কলঙ্ক হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করে তাঁদেরকে ঘৃণা করতে
শেখে। অন্যদিকে আবার মুসলিমরা শিক্ষিত হিন্দুদের মুখে কটুক্তি শুনে সমগ্র
হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলিম
দুই সমাজেরই একটি অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ এঁটে দিতে
তৎপর।৩
‘আনন্দ মঠ’ ও বঙ্কিম-বিদ্বেষের কারণ:-
বলা হয় যে, ‘আনন্দ মঠ’ উপন্যাসে ‘সন্তানদল’ মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে
যুদ্ধযাত্রা করেছে এবং গ্রন্থমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিমদের সম্পর্কে নানা
কটুক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। সন্তানদল ‘নেশাখোর নেড়েদের’ ‘বুকে পিঠে
চাপিয়া’ তাদের ‘সবংশে নিপাত’ করতে চেয়েছে, তারা মুসলিম গ্রাম ধ্বংস করছে,
‘যবনপুরী’, ‘বাবুই-এর বাসা,’ ও ‘শূয়োরের খোয়াড়’ ধ্বংসের আহ্বান জানিয়েছে এবং
‘মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির’ গড়তে চেয়েছে। সন্তানেরা চিৎকার করে বলছে-
“মার, মার, নেড়ে মার।” মহাপুরুষ বলেছেন-“তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলিম
রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই (৪।৮)।” তাঁদের মতে, ‘আনন্দ
মঠ’-এর এই সব অংশ এবং অন্যান্য রচনায় ইতিহাসকে বিকৃত করে সম্পূর্ণ
ইচ্ছাকৃতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হীনভাবে মুসলিম চরিত্র অঙ্কন করেছেন, মুসলিম শাসক ও
সেনাপতিদের কন্যাদের হিন্দুর প্রেম-পাত্রীতে পরিণত করেছেন এবং হিন্দু
চরিত্রগুলির প্রতি তিনি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বলা হয় যে, ‘বন্দে মাতরম্’
সংগীতটি “হিন্দুদেবী দুর্গার স্তব হিসেবেই রচিত হয়েছে” এবং তা “মুসলমানদের
বিরুদ্ধে অভিযানকারী সন্তানদের মুখ দিয়ে গাওয়ানো হয়েছে।” এই সব কারণেই মুসলিম
সমাজ সাধারণভাবে তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত। অনেকে আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে
‘সাম্প্রদায়িকতার জনক’ এবং ‘আনন্দ মঠ’-কে ‘শুভবুদ্ধিনাশক’ ও ‘দুর্গন্ধময়’
বলতেও কসুর করেন নি।৪ কেবলমাত্র ‘আনন্দ মঠ’ নয়- ‘রাজসিংহ’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’,
‘মৃণালিনী’, ‘সীতারাম’ প্রভৃতি উপন্যাস থেকে বিভিন্ন অংশ তুলে ধরা হয়েছে,
যেখানে তিনি মুসলিম-বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন। এই সব অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে
পাঠ করলে যে কোনো মুসলিম ক্ষুব্ধ হবেন এবং তা স্বাভাবিক।৫
হ্যাঁ, বিচ্ছিন্ন ভাবে পাঠ করলে তবেই ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু যদি উপন্যাস গুলি
সঠিক ভাবে পড়া হয়, বঙ্কিম রচনাকে পারম্পর্য অনুযায়ী উপলব্ধি করা হয় তাহলে
সহজেই একথা বোঝা যায় যে বঙ্কিম মুসলমান বিরোধী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রস
সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, ইতিহাস বা সমাজ চিত্র রচনা করা তার উদ্দেশ্য
ছিল না। ইতিহাসের উপকরণকে ঔপন্যাসিক অনেক সময় গ্রহণ করেন তথ্য প্রতিষ্ঠার
জন্য নয়; সাহিত্যের সত্য, চিরন্তন মানব সত্যকে রূপায়ণের তাগিদে। রবীন্দ্রনাথ
একেই বলেছিলেন তথ্য ও সত্য। এই সত্য রচনায় তিনি কাব্যের ভাষায় বলেছিলেন- ‘সেই
সত্য যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা তা সত্য নহে।’ ‘দুর্গেশনন্দিনী’ এই সত্য রচনার
উদ্দেশ্যে রচিত ইতিহাস-আশ্রিত একটি রোমান্স। এই জাতীয় উপন্যাসের বাস্তবতা
মিশ্র ধরনের। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়- “ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ
অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর
করে। জীবনের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝঙ্কারগুলি, জীবনের
বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ- ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু।… সামাজিক
উপন্যাসের সঙ্গে ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে
নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ
ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে।”৬ শুধু ‘দুর্গেশনন্দিনী’ নয়, অন্যান্য
রোমান্সধর্মী উপন্যাসে এই সূত্রই কাজ করেছে। তাই আয়েষা, মতিবিবি, কুলসম,
জেব-উন্নিসা, দরিয়া বিবি, গুরগণ খাঁ, তকি খাঁ জাতীয় চরিত্রগুলি বাস্তবতার
নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন রকমের আচরণ করেছে।৭
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সুযোগ সন্ধানীরা কতটা তৎপর হয়েছিলেন তার একটি কৌতুকাবহ
বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে
বঙ্কিমচন্দ্র একটি মুসলিম চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। নিশাকর নামে এক দুষ্ট
প্রকৃতির মানুষ এসেছিলেন গোবিন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে। এসময়ে গোবিন্দলালের
বাগানবাড়িতে দানেশ খাঁ নামে একজন মুসলমান গায়ক তানপুরায় আঙুল দিয়ে শব্দ
করছিলেন। নিশাকরের এক একটি কথা শেষ হওয়ার পর দানেশ খাঁ তানপুরায় এক দুই বলে
শব্দ করছিলেন। নিশাকর তখন কৌতুকচ্ছলে দানেশকে বলেন- “ওস্তাদ কি শূকর গুণছেন?”
তাতে দানেশ খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একথা বলা যেতে পারে যে নিশাকর ‘শূকর’-এর
বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারতো। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির নিশাকর কথাটির
ব্যবহার করেছে দানেশ খাঁকে বিরক্ত করার জন্যই। C.H. Philip সম্পাদিত
Historian’s of India, Pakistan and Cylon গ্রন্থে T.W. Clerk এই ঘটনা
সম্পর্কে লিখেছেন- “He is a casual and unimportant character of the plot for
which reason it is hard not to conclude that the author was seeking to
enhance the reputation of a Hindu character by presenting him with a
opportunity to affront a Mus-lim. What’s the singing master doing? Counting
Pig.”৮
বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্রকৃতই মুসলমান-বিদ্বেষী হতেন, তাহলে তাঁর উপন্যাসে এত বেশি
মুসলমান চরিত্র স্থান পেত না এবং তাঁদের অনেকেই আদর্শস্থানীয় চরিত্র। অন্যদিকে
হিন্দুদের মধ্যেও ভালো এবং মন্দ চরিত্র আছে। মুসলমান চরিত্রের মধ্যে তকি খাঁ
বা গুগণ খাঁর মতো ব্যক্তি যেমন আছে, তেমন মীরকাসেম বা চাঁদশাহ ফকিরও আছেন।
সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের উপসংহার অংশটি-
“গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে
করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের
উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু
হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই
আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু
ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ
ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ;
অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধৰ্ম্ম আছে- হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক- সেই শ্রেষ্ঠ।
অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই- হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক- সেই নিকৃষ্ট।”
বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যের স্রষ্টা। প্লট নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি
চরিত্রকে কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন। এজন্য পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মুসলমান
হিন্দু- উভয় শ্রেণীর চরিত্রই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে; এসেছে ইউরোপীয়ান
চরিত্রও। এরা সবাই ভালো নয়, আবার সকলে মন্দও নয়। হিন্দু চরিত্রের মধ্যে
‘কপালকুণ্ডলা’র কাপালিক, ‘বিষবৃক্ষ’-এর দেবেন্দ্র দত্ত কিংবা হীরা-র মতো
চরিত্র ভালো মানুষ নয়। ‘রজনী’র হীরালাল কিংবা ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর
‘দুৰ্দ্দান্ত পিতার অবাধ্য দুর্মুখ’ হরলালের মতো বহু চরিত্র সাহিত্যসম্রাটের
রচনায় স্থান পেয়েছে। গোবিন্দলালও ভালো মানুষ ছিলেন না। এর অর্থ এই নয় যে,
বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-বিদ্বেষী। ‘চন্দ্রশেখর’-এর লরেন্স ফস্টর বা আমিয়ট খারাপ
মানুষ। এদের দৃষ্টান্তে বঙ্কিমচন্দ্রকে খ্রিস্টানধর্ম বিরোধী বলা যায় না। মনে
রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই হাসিম
শেখকে রামা কৈবর্তের পাশে স্থান দিয়েছেন। আবার ‘মুচিরাম গুড়’-এর ষষ্ঠ
পরিচ্ছেদে ফেলু সেখ ও মিরজা গোলাম সর্ফদর খাঁর পাশেই মুচিরামকে বসিয়েছেন।
দেশের কল্যাণে ‘দ্বেষক ছাগ’কে বলি দিয়ে দ্বাদশকোটি ভূজে বঙ্গজননীকে দুর্গা
প্রতিমার রূপকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন ‘কমলাকান্ত’-এর “আমার দুর্গোৎসব”
প্রবন্ধে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে ছয়কোটি মস্তক ও বারো কোটি ভূজের উল্লেখ
করেছেন, তা কিন্তু কখনোই শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মস্তক বা ভূজ নয়,
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের।
তবু কেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ? কেন তার বিরুদ্ধে এত বিষোদগার?
এর কারণ কিন্তু বঙ্কিম স্বয়ং এবং অপর একটি কারণ তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি।
মাননীয় রতন কুমার নন্দী লিখছেন, ” বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানের লেখক নন, ইতিহাসে
বঙ্কিমচন্দ্র বারবার জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। প্রথমে
উপন্যাস এবং পরে বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে সত্যই তিনি বাঙালি পাঠকের ‘হৃদয় একেবারে
লুঠ’ করে নিয়েছিলেন। ফলে অন্য কোনো লেখক হিন্দু বা মুসলমান চরিত্র নিয়ে কি
লিখেছেন সে সম্পর্কে কোনো সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।
বঙ্কিম-সাহিত্যের যাঁরা সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়
সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। বোঝা যায় এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা মনোযোগ সহকারে
পাঠ করেছেন।
হতে পারে তাঁদের মতামতে বিরূপতা আছে; কিন্তু তা প্রমাণ করে এই সমালোচকেরা
বঙ্কিমচন্দ্রকে নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন।”৯
তৎকালীন সময়ের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর
ধীরে ধীরে
বাংলায় মুসলমান শাসন আলগা হতে থাকে; পরে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয়ের
পর প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও আরও পরে ব্রিটিশ সরকার বাংলার শাসন ক্ষমতা
করায়ত্ত করে। উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় আইন-আদালত, সরকারি অফিস, স্কুল কলেজ
স্থাপনের সুফল হিন্দু সমাজ যেভাবে গ্রহণ করেছিল, মুসলমানেরা সেভাবে গ্রহণ করতে
পারেনি। কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের সুফল লাভ করেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত
বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা। মুসলমানেরা প্রথমে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করতে
পারেনি, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সভাসমিতি থেকেও তারা নিজেদের সরিয়ে রাখে।
এসময় “… সব হারানো মুসলমান তখন ধর্মের ছায়াতেই আশ্রয় খুঁজছিল। সমাজে ধর্মীয়
পরিচয়কে আঁকড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা তাঁদের মাঝে দ্রুত বর্ধিত হয়।
হান্টারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে
মুসলমানরা পোশাক-আশাক, অভিবাদন পদ্ধতি এবং বহিরঙ্গে সব বিষয়েই হিন্দুদের থেকে
পৃথক এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে।” ১০
এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন- “During the first half of
the 19th century they (ইংরেজ শাসক) favoured the Hindus against the Muslims,
and during the next they put on foot on the other leg and stirred of the
Muslims against the Hindus.”১১
প্রসঙ্গত ওয়াকিল আহমদের একটি অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে- “হিন্দু প্রভুর বদল
হয়। মুসলমানের প্রভুত্ব যায়। প্রভুত্ব হারানোর বেদনা তাদের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ
করে তোলে। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দুগণ অনুগামী ও মুসলমান
পশ্চাৎগামী হলেন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ মুসলমান হওয়ায়, প্রলুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়কে
অধিক নির্বিষ, বিশ্বস্ত ও অনুগত মনে করলেন।”১২
এর ফলে নগরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত, তৎকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক
কেন্দ্রভূমি কলকাতায় যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্থানটির দখল করে হিন্দু
সমাজ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে ভাববিপ্লবের
সূচনা হয়, তার নেতৃত্বে ছিল হিন্দুরাই। বিদ্যাচর্চা, ইংরেজের সহযোগী হয়ে
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রগতিশীল সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রণী
ভূমিকা পালন করে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর তৈরি
হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমান সমাজের একাংশ পুরোনো অবস্থান
থেকে সরে আসতে থাকে। নব্য শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের রচনায়
স্বধর্মের প্রতি অনুরাগের তীব্রতার সঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষেরও সূচনা হয়।
সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও এর প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যকে
পরিহার করে আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা রচনায় তাঁরা সচেষ্ট হলেন। এই ভাষাই
‘মুসলমানী বাংলা’ নামে একসময় অভিহিত হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ লং ফ্রেন্ড
অফ ইন্ডিয়া-য় প্রথম ‘মুসলমান বেঙ্গলী লিটারেচার’ শব্দটি ব্যবহার করেন। যা থেকে
পরবর্তীকালে ‘মুসলমানী বাংলা’ শব্দটি প্রচলিত হয়।
পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন। আরব দেশে মহম্মদ
আবদুল ইবনে ওয়াহাব নামে একজন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য আন্দোলনের
সূচনা করেছিলেন। রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ নামে এক ব্যক্তি আরবে হজ করতে গিয়ে তাঁর
সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর মতবাদে প্রভাবিত হন। ভারতে ফিরে এসে অনুগামীদের নিয়ে
তিনি এই আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলাম ধর্মকে যথার্থ পথে
ফিরিয়ে আনলেই সমাজ শক্তিশালী হবে। এর মাধ্যমে দার-উল-হাব থেকে ভারতকে মুক্ত
করে দার-উল-ইসলাম-এ পরিণত করা সম্ভব হবে। এর পরেই শুরু হয় ফরাজি আন্দোলন।
ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লা এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ‘ফরজ’ কথাটির অর্থ
অবশ্য করণীয় কাজ। বোঝাই যায় শরিয়তি মতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ফিরিয়ে আনাই ছিল
ফরাজিদের লক্ষ্য।১৩
বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এই দুই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে চণ্ডীপ্রসাদ সেন
‘বাঙালি মুসলমান’ গ্রন্থে লিখেছেন- “বাংলায় ওয়াহাবি ও ফরাইজি- এই দুই ধর্মীয়
পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অতীতের শুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তন। এবং
এদেশে কোরাণ নির্দিষ্ট একেশ্বরবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ঐ আন্দোলনের
প্রবক্তারা তাঁদের লক্ষ্য লাভেই শুধু ব্যর্থ হয়েছিলেন তা নয়, তাঁদের এই
আন্দোলন পশ্চিমী সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ
সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অনীহাই সৃষ্টি করেছিল।” ১৪
ফলে শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, বাঙালি হিন্দুর সাহিত্য সম্পর্কেও এঁদের বীতশ্রদ্ধ
করেছিল।
ঠিক এই সময়ে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিপরীত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।
বঙ্গদর্শন প্রকাশ-পরবর্তী যুগের প্রবণতাকে সুকুমার সেন বলেছেন- ‘চিত্ত
সংস্কারের যুগ’ “চিত্ত সংস্কারের একটি বড়ো প্রকাশ হইল ‘জাতীয়’ বোধের উন্মেষে,
স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণে। গদ্যে পদ্যে নাটকে প্রবন্ধে তর্কে, অভিনয়ে
বেশে-ব্যবহারে চিন্তায় কর্মে এই সম্প্রদায়ের মর্মকথাটি প্রকাশোন্মুখ হইয়াছিল।”
১৫ এই সময়ে বাঙালির মধ্যে স্বদেশী ভাবের জাগরণ তৈরি হতে থাকে। যদিও এর সূচনা
হয়েছিল কিছু আগে থেকেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন-
“তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়।
অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে
সর্ব্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।১৬
সিপাহি বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের ফলে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে
অস্থিরতা দেখা দেয় তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। নব্যশিক্ষিত
উৎসাহীদের মধ্যে জাগ্রত হল জাতীয় চেতনা, প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু মেলা। হিন্দু
মেলা শুরু হওয়ার পর দেশে স্বদেশ প্রেম প্রবল গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো। হিন্দু
মেলার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে- “অতএব সেই
সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না।
সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম। সেই স্বজাতি ধর্ম আমাদের অজ্ঞানতারূপ
অন্ধকার কারাগারে পারবশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্বপ্রযত্নে
বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আত্মনির্ভর নামা শাণিত অস্ত্রধারা পারবশ্যরূপ
শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে
অদ্বিতীয় উপায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য।”
এই যুগ পরিবেশেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টিতে নিমগ্ন ছিলেন। অনেকের মতে সেটা
ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পর্ব। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে এর যাত্রা
শুরু। বলা যায় তার পূর্বেই খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে সংঘাতে রামমোহন রায়,
দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা যা শুরু করেছিলেন তা রূপান্তরিত
হল সাহিত্যে, ধর্মে এবং স্বাদেশিক আন্দোলনে। সাহিত্যে এই ধারার শুরু করেছিলেন
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেই পথই অনুসরণ করলেন।
মধুসূদন রামায়ণ বা অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিকে নবভাষ্য দান করলেও তাঁর আকর ছিল
হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। বাংলা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকেও হিন্দুত্বের মাধ্যমে
দেশাত্মবোধ সঞ্চারের চেষ্টা চলছিল। স্মরণীয়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে অনেকেই
তখন হিন্দু কংগ্রেস বলে মনে করতো। বিদেশি জাতির সঙ্গে এই যে বিরোধ, যা
হিন্দুত্বকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল, সেটাই গুরুত্ব পেল বঙ্কিমচন্দ্রের
উপন্যাসে-প্রবন্ধে। আর এই সময়ই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে মুসলমান সমাজে পুনর্জাগরণের
সঞ্চার হয়েছিল, যা একসময় হিন্দু বিরোধিতা তথা বঙ্কিম-সাহিত্যের বিরোধিতায়
পরিণতি লাভ করে।১৭
এবার আমরা বেশ কিছু মুসলিম লেখকদের লিখিত বক্তব্য জেনে নেব, যাঁরা সাহিত্য
সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁরা
স্পষ্টত ব্যক্ত করেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিরোধী ছিলেন না বরং তাঁর
রচনায় তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সৎ ও অসৎ রূপ সমান ভাবে তুলে ধরেছেন।
সর্বপ্রথম কাজী নজরুল ইসলামের ‘ বঙ্কিমচন্দ্র ‘ প্রবন্ধ তুলে ধরি-
” রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের ভারতের দুর্ভাগ্য-তিমির ঘেরা গগনের রবি হন,
বঙ্কিমচন্দ্র তাহলে সেই তিমির রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বাশা, সেই রবির অগ্রগামী
উদয়তারা। আর বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যে সব প্রতিভার
বরপুত্রের আবির্ভাব হয়েছে-বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের আদিস্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে
না- এই সব জ্যোতিষ্কের সৃষ্টির বীজ তাতেই লুকিয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর
পরবর্তী সমস্ত কবি সাহিত্যিকের পিতামহ ব্রহ্মা।
কেরোসিনের ডিবের আলোকে যারা মানুষ, বিজলি বাতির অতি-দীপ্তি যেমন তাদের
চক্ষু-পীড়ার কারণ হয়, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতির্ময় প্রতিভা তাঁর সমসাময়িক
সাহিত্যিকদের চোখ ঝল্সে দিয়েছিল- তাই তাঁরা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করার বদলে
অভিসম্পাতই বেশী করেছিলেন। সে সময় বাঙলা ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে আসতে হ’লে
সংস্কৃতের সাধুদের টিকি বিসর্গের চন্দন-ফোঁটা এবং যুক্তাক্ষরের ইষ্ট নামাবলী
পরে আসতে হ’ত। সে ভাষার যে রূপ তাতে বাইরে তাকে ব্রাহ্মণ বলে মনে হ’লেও ছিল,
রসহীন রূপহীন অসংস্কৃত। তাকে বাঙলা ব’লে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙলার
বাণীমন্দির থেকে এই পাণ্ডাদের বিতাড়িত করেন। খঙ্গ-হস্ত গুম্ফ-শ্বশ্রু-কর্কশ
বাঙলা ভাষা এঁরই প্রসাদে বেণুবীণা ও পূর্ণশ্রীর প্রথম প্রসাদ পেল। ইনিই
সংস্কৃত-জহ্নুর জঙ্ঘা থেকে বাঙলাভাষার রস-গঙ্গা রূপকে উদ্ধার করেন। বাঙলা তাঁর
কাছে চির-কৃতজ্ঞ। শ্রী সরস্বতীর অধিপতি এঁরই সাধনায় ঠুটো জগন্নাথ রূপের মুখোশ
খুলে পূর্ণসুন্দর প্রেম-ঘন রস-ঘন আনন্দ-ঘন পূর্ণ রূপশ্রী কান্তি লাবণ্য মাধুরী
নিয়ে ষড়ৈশ্বর্য্য বিভূষিত শ্রীনারায়ণ দেখা দেন।
অবশ্য এর আগে যে সব বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনা করে গেছিলেন, তা আনন্দ
বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন চিরকিশোর পূর্ণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের রূপই প্রকাশ
করেছে। এর অধিকারী ছিলেন কেবল তাঁরা- যাঁরা নিত্যধামের তীর্থ-পথিক। যাঁদের এ
পরমতৃষ্ণা আসেনি, তাঁরা এই অমৃতকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন সৃষ্টি
স্থিতি সংহারে যে সত্য মিথ্যা আলো অন্ধকারের খেলা- তারই রূপ দেখতে। কিশোর হরির
সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় রূপকে সাহিত্যে প্রকট করলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ
প্রেমে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বদ্ধ জীবকে তার বন্ধন অবস্থাতেই
হাসালেন কাঁদালেন, তাদের অন্তরের স্বরূপ বাইরের স্বরূপ নিখুঁত করে এঁকে
দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই মনীষী ঋষি। যে পুকুরের জলের সাগরের দিকে টান নেই
সেখানে আনন্দের পদ্ম শালুক ফুটালেন- তার চারধারের বাঁধ ভাঙবার শক্তি ও তৃষ্ণা
জাগালেন। তাঁর এই বিপুল শক্তির প্রাচুর্যই ‘বন্দে মাতরম্’ গানের বাণীতে প্রকাশ
লাভ করল। যে সপ্তকোটি বাঙালীকে অনাগত মহাভারতের অগ্রদূত বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন-
এই গানের মন্ত্রশক্তি তা সারা ভারতে প্রাণ সঞ্চার করল। অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে
অনেকের মতভেদ থাকলেও একথা আজ অস্বীকার করতে পারব না বাঙালীর ঘুমন্ত বদ্ধ মনকে
তিনি আচমকা ভূমিকম্পের মত এসে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।
আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদেরও তিনি গুরু বললে অত্যুক্তি হবে না।
নেতারা কর্মী- কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। রসহীন শ্রান্ত জীবনে শিক্ষিত
বাঙালী নূতন রস আনন্দ পেয়েছিল। সাহিত্য কাব্য প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্পই
বিলাসী মনের খাদ্য, কর্মক্লান্ত মনকে আনন্দ দিয়ে তাজা রাখে এই আনন্দরস। জীবনে
এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রস-বিলাসেই মত্ত থাকেননি,
শক্তিহীন জাতিকে শক্তি দিয়েছিলেন, গুরুর মত তাদের ত্যাগের পথে বৈরাগ্যের পথে
মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিলেন।
তার আশেপাশে তাঁরই আত্মীয় অনাত্মীয় রূপে যারা ঘিরেছিল তাদের পূর্ণ স্বরূপ তাঁর
মনের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হয়েছিল- তারই রূপ তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে
উঠেছে। শুধু তাদের বাইরের রূপ নয়, মনের আত্মার বেদনা ক্রন্দন তিনি দেখেছিলেন,
শুনেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাস কখনো পুরাতন হ’ল না হবে না। আজো তাঁর
কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ বাঙালীর পুরানো হল
না। যত পড়ি, ততই রস পাওয়া যায়। এইখানে হয়ত তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।
আধুনিক সাহিত্যিকরা যেখানে কেবল বুদ্ধির চাতুর্য, লিখনভঙ্গীর অপূর্ণতায় কেবল
জ্ঞানকে মুগ্ধ করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সে জ্ঞানশক্তি নিত্য রসায়িত। তিনি
মানুষের অন্তরতম কোণে গিয়ে খেলা করেছেন- যেখানে প্রেম ছাড়া, জ্ঞান কখনো যেতে
পারে না। জ্ঞানকে মাথায় রাখি, প্রেমিককে রাখি বুকে তাকে বাঙালী মাথায় না রেখে
বুকে রেখেছেন- সেইখানেই তাঁর আসন নিত্য।”১৮
মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ -এর মতে,-
“আজ হরিজন আন্দোলনের দিনে বঙ্কিমের এই সামাজিক দুর্গতির নিদান বিশেষ মনোযোগের
সহিত আমাদের অনুধাবন করা কর্তব্য।
জমিদার ও রায়তের বৈষম্য বঙ্কিমের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল। তাই তিনি বড় দুঃখে
বলিয়াছিলেন- “জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু
বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহৎ জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে ভক্ষণ
করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক
নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন
না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।
কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুৰ্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী
বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু
তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন
না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।”
রায়তের দুর্দশা দেখাইবার জন্য তিনি যে পরাণ মণ্ডলের করুণ চিত্রটি আঁকিয়াছেন,
তাহা একবার সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি। দীর্ঘতার ভয়ে আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত
করিতে অক্ষম। আজ কৃষক আন্দোলনের যুগে ইহা বারংবার পাঠ করার প্রয়োজন আছে।
তিনি বুঝিয়াছিলেন এই কৃষকের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। তাই তিনি
বলিয়াছেন- “আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।
এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য
হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।…
“এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম
শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার
উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে,
উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায়
ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কদম পান করিতেছে;
ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা যাইবে না, এই চাষের
সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা
বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেড়া মাদুরে, না হয় ভূমে,
গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে- উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই
এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে- যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে
ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময়
জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস- সপরিবারে
উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু। ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া
ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে
হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ
শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ-তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর
রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?
“আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে
মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার
আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই
কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই
দেশ- দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে
পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে
তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।”
আপনারা দেখিলেন, পরাণ মণ্ডল বা রামা কৈবর্তের জন্য বঙ্কিমের যতটুকু দরদ, হাসিম
শেখের জন্যও ততটুকু। এখানে কোন হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নাই। এই হিন্দু মুসলমান
সম্পর্কে বঙ্কিমবাবু অন্যস্থানে বলিয়াছেন-
“আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে?
বাবাজী। এ-কান দিয়া শুনিস, ও-কান দিয়া ভুলিস? যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে
আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি,
এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।” আর এক
স্থানে তিনি বলিয়াছেন-
“গড বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের
অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার
আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে
যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে,
লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মরিতেই ব্যস্ত,
তাহার গলায় গোচ্ছাকরা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে
নামাবলি, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম
ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।” যেদিন হিন্দু
বঙ্কিমের এই বৈষ্ণবের মত গ্রহণ করিবে, সেদিন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা থাকিবে না,
সে শুভ দিন কবে আসিবে?”১৯
কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁর লেখায় বলেছেন, –
”
যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা, অর্থাৎ মুসলমান-বিদ্বেষ, সে-অপরাধে তাঁকে
সহজেই অপরাধী না ভাবা যায় এই বিবেচনা থেকে যে মীরকাসেম, দলনী বেগম, চাঁদশা
ফকির, ওসমান, আয়েষা প্রভৃতি কয়েকটি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে উৎকৃষ্ট মুসলমান
চরিত্র তাঁর কলম থেকে উৎরেছে; আর “বঙ্গদেশের কৃষকে” ও “সাম্যে” তিনি যাদের
পক্ষ অবলম্বন করেছেন তারা জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির
ভিতরে একটি ঔদ্ধত্য ছিল- হ’তে পারে সেটি শক্তির ঔদ্ধত্য- সেই ঔদ্ধত্য সহজেই
যুদ্ধং দেহি বলে’ দাঁড়িয়েছে বিজেতার ঔদ্ধত্যের সামনে তা সে বিজেতা সেকালের
মুসলমানই হোক আর এ কালের ইংরেজই হোক, আর তাঁর দেশের লোক বা সম্প্রদায়ের লোক
এই বিজেতাদের সামনে যত হীনপ্রভই হোক- তাঁর তথাকথিত বিদ্বেষ সম্পর্কে এই-ই
যথার্থ কথা বলে মনে হয়। কিন্তু মুসলমান নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের
অপরাধ তাঁর না থাকলেও হিন্দু নামে আর একটি সম্প্রদায়ের ভালোর জন্যে তাঁর যে
মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা প্রতিভাবান্ হিসাবে সেটি তাঁর একটি অপরাধ। স্বজন
বাৎসল্য সাধারণতঃ মানুষের ভিতরে প্রবল এ উত্তর এখানে উত্তর নয় কেননা
বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাছে একজন জ্ঞানব্রতী সাহিত্যিক যাঁদের কাছে মানুষ কামনা
করে এবং পায় স্বজনবাৎসল্যের চাইতে উঁচুদরের জিনিষ তার নাম সত্যাশ্রয়িতা আর
মানবতা। এ কথার ভুল অর্থ সহজেই করা যায় এই ভেবে যে আমরা সাহিত্যে একান্তভাবে
নির্বিশেষের সাধনার কথা বলছি। সেকথা বলা সম্ভবপর নয় কেননা, বিশেষকে নিয়েই
সাহিত্যের চিরদিনের কারবার, নির্বিশেষের দ্যুতি আপনা থেকে যাতে খেলে। কবির
কথায় এ ব্যাপারকে বলা যায়- ‘ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।’ এই অবিরাম যাওয়া
আসায় ব্যাঘাত ঘটলেই সাহিত্যসৃষ্টি অসুন্দর অর্থাৎ অসার্থক হয়। দেশকালের বিশেষ
রূপ যাতে না ফুটেছে তা সাহিত্য হয়নি একথা যতখানি সত্য সেই দেশকালের রূপে
সত্যাশ্রিয়তার ও মানবতার চিরন্তন দ্যুতি যদি না ফুটে থাকে তবে তাও সাহিত্য
হয়নি এও ততখানি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্বের জয়ঘোষণা যত উচ্চকণ্ঠেই করে’
থাকুন সার্থক জয়ঘোষণা তিনি যা করতে পেরেছেন তা সত্যের আর মানুষেরই- আর
সেইজন্যই তিনি প্রতিভাবান্- তাঁর রচনা একটু বিশ্লেষণ করে’ দেখলে তা বোঝা কঠিন
হবে না।
বুঝতে চেষ্টা করা যাক তাঁর আনন্দমঠের হিন্দু শক্তির পুনরুত্থানতত্ত্ব যার
জন্যে অসম্ভব রকমের স্তুতি আর নিন্দা তাঁর লাভ হ’য়েছে। ধ্বংসোন্মুখ মুসলমান
রাজশক্তি হিন্দু বিদ্রোহীরা নির্মূল করতে চেষ্টা করলে মনের সাধ মিটিয়ে, এ
পর্যন্ত কিছু পরিমাণে বোঝা গেল হিন্দু শক্তির পুনরুত্থানের কথা। কিন্তু সেই
বিদ্রোহীদলে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল নানা ত্রুটি- হিন্দুরাজ্য স্থাপন তাদের
দ্বারা হ’লো না। এই বিদ্রোহীদের নেতা সত্যানন্দের মনোদুঃখেরও আর অন্ত রইল না।
তখন বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি নিৰ্দ্দেশ করলেন সুদূর ভবিষ্যতের পানে যেখানে হিন্দু
শক্তির পুনরুত্থানের একান্ত সম্ভাবনা রয়েছে লোকশিক্ষক ইংরেজের আনুকূল্যের ফলে।
কিন্তু সেই ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে তিনি হিন্দুত্ব বল্লেন কাকে?- “তেত্রিশ কোটী
দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধৰ্ম্ম… হিন্দু ধৰ্ম্ম
জ্ঞানাত্মক”- হিন্দুত্বের এই সংজ্ঞা তিনি দিলেন চিকিৎসকের মুখে। কিন্তু এ
সংজ্ঞা বাস্তবিকই হিন্দুত্বের বিশেষত্বের পরিচায়ক হ’লো না। ধৰ্ম্ম জ্ঞানাত্মক
কৰ্ম্মাত্মক নয়- এ মত অনেক ধৰ্ম্মসাধক তাঁদের নিজ নিজ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধেও
দিয়েছেন। তা ছাড়া “তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা অপকৃষ্ট
লৌকিক ধর্ম”- একথা বলে তিনি হিন্দু ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে এমন একটি মত দিলেন যা
হিন্দু ধর্মের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতার মতের বিরুদ্ধ। এ কালের স্বনামধন্য
রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা ভাবা যাক। “তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে” এ
পর্যন্ত এঁর সঙ্গে বঙ্কিমের বিরোধ নেই; কিন্তু “সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধৰ্ম্ম”
একথা রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞানতার পরিচায়ক। তা ছাড়া
ব্যাপকভাবে হিন্দু সমাজ একথা স্বীকার করছেন না যে “তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা
একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধৰ্ম্ম”। এবং যাঁরা এমন কথা বলেছেন যেমন ব্রাহ্মসমাজের
নেতৃবৃন্দ, তাঁদের তাঁরা ভাবেন অনাত্মীয়। তেমনি ভাবে অদ্ভুত তাঁর
কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা ভক্তহিন্দুর চোখে। ভক্তির তন্ময়তার স্বাদে তিনি
বঞ্চিত এ ভিন্ন আর কিছু যে তাঁর সম্বন্ধে ভক্তহিন্দুরা ভাবেন তা মনে হয় না।
কিন্তু হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ
হ’লেও বাস্তব পক্ষে তা কম অর্থপূর্ণ নয়। তিনি নিজেকে হিন্দুর যতো বড়ো
উদ্ধারকর্তাই মনে করুন প্রকৃত কথা এই যে তিনি হচ্ছেন বিশেষ ভাবে তাঁর যুগের
সন্তান- তাঁর যুগে সভ্যজগতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সব সাধনা চলেছিল তিনি সে সবের
সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত; আর সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের শক্তিতে তিনি দূর করতে
চেয়েছিলেন তাঁর চারপাশের লোকদের ভাবালুতা, স্পষ্ট নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন
তাদের জাগতিক জীবনে শ্রেয়োলাভের- চিরকালই কর্মী ও চিন্তাশীলেরা যা ক’রে থাকেন।
মানুষের মুখের কথায় আর অন্তরের প্রবণতায় বিরোধ অবশ্য সুপরিচিত, সেইসঙ্গে আরো
বুঝতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান, মোহ আর মোহমুক্তি এই দুইয়ের
ধ্বস্তাধ্বস্তি যে-যুগে উৎকট আকার ধারণ করেছিল।
হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম-সাহিত্যে যতই থাকুক তাঁর সত্যকার প্রতিপাদ্য
হিন্দুত্ব নয় মানবতা- একথা আরও স্পষ্ট করে’ বোঝা যায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথা
ভাবলে। তাঁর রাজসিংহের বিখ্যাত বা কুখ্যাত জেবুন্নিসা চরিত্রের কথা ভাবা যাক।
তাঁর জেবুন্নিসা তাঁরই জেবুন্নিসা, ইতিহাসের জেবুন্নিসা নয় সাহিত্যশাস্ত্রে এ
একরকমের স্বতঃসিদ্ধ। আর এই জেবুন্নিসা-চরিত্র তিনি হীন করে’ এঁকেছেন না
উৎকৃষ্ট করে’ এঁকেছেন তাও নির্দ্ধারিত হ’তে পারে সাহিত্যিক বিচারের দ্বারা
অন্য কোনো বিচার পদ্ধতির দ্বারা নয়। জীবনে প্রকৃতভাবে হীন সেই যে তেজোহীন,
সাহিত্যেও তেমনি হীন চরিত্র সেটিকে বলা যায় যা লেখকের অনুরাগ পুষ্ট নয় সুতরাং
পাঠকদেরও অনুরাগ আকর্ষণে অক্ষম। কিন্তু সমঝদারদের চোখে জেবুন্নিসা চরিত্রটির
মাথাই তো জেগে উঠেছে রাজসিংহ উপন্যাসের সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি-অভিসন্ধির
উর্দ্ধে। লেখক এঁকে প্রথমে পাঠকদের সামনে এনেছেন স্বেচ্ছাচারিণী দানবীরূপে;
কিন্তু পরে পরে পরম যত্নে পরম কৌতূহলে তিনি দেখিয়ে চলেছেন এই দানবীর
মর্ম্মবাসিনী প্রেমময়ী মানবীকে। রাজসিংহের উপসংহারে এমন দুই একটি কথা তিনি
বলেছেন যা থেকে বোঝা যায় জেবুন্নিসাকে তিনি ভালো ভাবেন নি। কিন্তু
চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকেও তিনি বলেছেন পাপীয়সী, আর আনন্দমঠের ভবানন্দকে
কল্যাণীর মুখে বলেছেন দুরাচার পামর। অথচ যাদের তিনি সাধারণ বিচারে সাধু ও
সাধ্বী করে’ এঁকেছেন তাদের সঙ্গে তুলনায় জেবুন্নিসা, শৈবলিনী, ভবানন্দ, তাঁর
এই তিনটি অসাধু চরিত্র সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে কত বেশী গৌরবময়।
মানবচরিত্রজ্ঞানের, মানুষের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তার, কত গভীর পরিচয় এসবে রয়েছে।
অথচ তাঁর এই দুর্লভ সাহিত্যিক শক্তিও কম বিড়ম্বিত হয়নি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত
হিন্দুত্বের দ্বারা। তাঁর শেষ বয়সের কয়েকখানি উপন্যাসে তাঁর অঙ্কন-কৃতিত্ব
যথেষ্ট প্রকাশ পেলেও মোটের উপর তাঁর দৃষ্টি অতীতমুখী। অমোঘ বিশ্ববিধানে যে
জীবন হিন্দুরও জন্য সত্য হয়েছে বা হ’তে চলেছে তার প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে অতীতের
মোহ যে তাঁর হৃদয় বেশী অধিকার ক’রেছে এ জন্য তাঁর এই সব রচনা হয়েছে অনেকখানি
সৌখীন- হিন্দুরও জন্য তা অনিষ্টকর ভিন্ন আর কিছু নয় যদি হিন্দু এসবের এই
অন্তনির্হিত ভাববিলাস সম্বন্ধে সজাগ না থাকে।
বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সুষ্পষ্ট দ্বন্দু আছে মনে হয়। সহজ
ভাবে তিনি জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পূজারী, আবার প্রবল ভাবে তিনি হিন্দুত্বের
প্রচারক। এই প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাকীৰ্ত্তনই এতদিন বিশেষভাবে হ’য়েছে।
তার কারণও বোঝা যায় সহজে। বাংলাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু আর মুসলমান।
উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুয়ের মধ্যে এক বড় রকমের ব্যবধান দেখা দিল। মুসলমান দল
করলে নবরাজশক্তির সঙ্গে প্রবল বিরোধিতা, হিন্দুদল করলে প্রাণঢালা মিতালি।
নিজেদের বিরূপতা আর রাজশক্তির অপ্রসন্নতা এই দুইশক্তির একমুখীটানে
প্রাধান্য-গর্বিত মুসলমান-দল অন্তর্হিত হয়ে গেল দেশের আমদরবার থেকে, সেখানে
আসর জমলো দীর্ঘদিনের অবহেলিত হিন্দুর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অবসানের
সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে বাংলার প্রধান অধিবাসী হ’লো হিন্দুই। এহেন
পরিবেষ্টনে হিন্দুত্বের নব অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের প্রসার শুধু
স্বাভাবিক নয় প্রায় অনিবার্য। এযুগের হিন্দু সমাজের প্রায় প্রত্যেক
মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তিই এই হিন্দুত্বের নবজাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন-অবশ্য
বিভিন্নভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁর মতো মনীষা ও
সহজ মানবতা সম্পন্ন ব্যক্তি এই সাময়িক মোহে এত বেশী বিভ্রান্ত হ’য়েছেন।
আমরা যে দৃষ্টিতে বঙ্কিম-প্রতিভার দিকে তাকাচ্ছি কেউ কেউ তাকে আগাগোড়া ভুল
বল্লে পারেন। তাঁদের বক্তব্য এই ধরণের:- হিন্দু আর মুসলমান দীর্ঘকাল এদেশে
একসঙ্গে বসবাস করছে, মারামারিও তারা করছে আজ থেকে নয়- এ মারামারি থামলো না।
এমন বিরোধের পরিণতি অন্যান্য বহুদেশে যেমন হয়েছে ভারতেও তার ব্যত্যয় হবে মনে
হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ও ইকবালের শক্তিশালী সাহিত্য হয়তো সেই নিৰ্ম্মম কিন্তু
অমোঘ বিধিলিপি।
এই ধরণের চিন্তা সহজেই মনে হ’তে পারে অত্যন্ত বাস্তবমুখী বলে। কিন্তু প্রকৃত
প্রস্তাবে এটি তা নয়। হিন্দু আর মুসলমানের এমন শক্তিপরীক্ষার দিন- এর অভিনয়
মাত্র নয়- আস্তে পারে সত্যকার রাজনৈতিক অধিকার যদি তাদের লাভ হয়। কিন্তু এমন
অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের মনোভাবের নিত্যসঙ্গী ভয়- আর সেই ভয়ের অপরিহার্য্য গতি
কোনো তৃতীয় পক্ষের আনুকূল্যলাভের দিকে। এইভাবে একটু বিচার করে’ দেখলেই বোঝা
যায়, এই তথাকথিত বাস্তবমুখী চিন্তাধারা থেকে কোনো রকমের শক্তিলাভ দেশের লোকের
পক্ষে দুরাশা মাত্র; এর থেকে তাদের লাভ হ’তে পারে কেবল শক্তির অভিনয়-কুশলতা-
যথা, সভাসমিতিতে পরস্পরের প্রতি কটূক্তি-বর্ষণ, সময় সময় কিঞ্চিৎ লাঠালাঠি ও
ইটপাটকেল বৃষ্টি ইত্যাদি। নিয়তি চির অজ্ঞাত, মানুষের জন্য কাম্য যা উৎকৃষ্ট
বিবেচিত হয়েছে তার সাধনা। ২০
বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীরেজাউল করিম তাঁরন প্রবন্ধে বলছেন-”
সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে এক জন যুগপ্রবর্তক সাধক ছিলেন তাহা সকলেই
একবাক্যে স্বীকার করে। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার উপর শ্লেষাত্মক টীকাটিপ্পনী
করিবার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক জন শ্রেষ্ঠ সংগঠক বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে
কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। সুতরাং এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক
সাহিত্যরসিক তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য প্রকাশ
করিবেন না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, অনেক মুসলমান সাহিত্যিক
বঙ্কিমকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন; কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে
বঙ্কিমচন্দ্র এক জন ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা না কি বঙ্কিমের বিরাট্
সাহিত্য-ভাণ্ডারে মুসলিম-বিদ্বেষের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। এক্ষণে
আমাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, বঙ্কিম-সাহিত্যে
মুসলিম-বিদ্বেষের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃতির বিদ্বেষ,
তাহার স্বরূপ কি? তাহা বাস্তবিকই মুসলিম-বিদ্বেষ, না আর কিছু?
বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম-বিদ্বেষী, আর তাঁহার সাহিত্য মুসলিম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ-
এই অভিযোগ কে করিল ও কবে করিল? বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বহু যুগ
পূর্ব্বে। তাঁহার কোন গ্রন্থে কেহই কোন পরিবর্তন করে নাই। তিনি যে-আকারে
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, আমরা আজিও তাহা সেই আকারে পড়িয়া থাকি। তৎসত্ত্বেও
এত যুগ ধরিয়া তাঁহার গ্রন্থমালা সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর মত তাহা
মুসলমানও পড়িয়াছে, শিখিয়াছে এবং নির্বিচারে অনুসরণ করিয়াছে এবং সকলেই তাঁহাকে
একবাক্যে সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু এত দিন তাঁহার
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠে নাই, আজ উঠিবার কারণ কি? এত দিন যে-বিদ্বেষকে কেহই
আমল দেয় নাই, তাহাই লইয়া আজ কেন এত আন্দোলন উঠিতেছে? বঙ্কিম-সাহিত্যে তথাকথিত
মুসলিম-বিদ্বেষের পরিচয় আছে সেই জন্য, না অন্য কারণে? বঙ্কিমের যে গ্রন্থকে
সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুসলিম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই ‘আনন্দমঠ’
প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তর্কস্থলে ধরিয়া লইলাম যে, ‘আনন্দমঠ’ মুসলিম-বিদ্বেষে
পরিপূর্ণ, উহা ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজ স্থাপনের জন্য উদ্দীপনা জাগাইবার
উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উপেক্ষা করিলে চলিবে
না। ‘আনন্দমঠ’ হিন্দুকে মুসলিম-বিদ্বেষী করিতে সাহায্য করিয়াছে, না জাতীয়তার
আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছে? ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশিত হইবার অল্প দিন
পরেই উহা এরূপ লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল যে, তাহার তুলনায় অন্য কোন পুস্তক
টিকিতে পারে নাই। বাংলার বহু লোক ‘আনন্দমঠ’ পাঠ করিয়াছিল, আদর করিয়াছিল এবং
উহার আদর্শ অনুযায়ী দল গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।
কিন্তু তাহাতে মুসলিম-বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র ছিল না। সুতরাং অনায়াসে বলা যাইতে
পারে যে, ‘আনন্দমঠ’ হিন্দুকে মুসলিম-বিতাড়নের আদর্শে দীক্ষিত করে নাই, দীক্ষিত
করিয়াছে স্বদেশ-মন্ত্রে।
বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষের স্বরূপটা বিচার করিবার পূর্ব্বে আর একটা
বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সাহিত্য-বিচার করিবার মানদণ্ড কি? সাহিত্যের একটা
ধৰ্ম্ম আছে, আদর্শ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সেই ধৰ্ম্ম, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ব্যতীত
কোন রচনাই সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।
রসসৃষ্টি সাহিত্যের একটি প্রধান ধৰ্ম্ম। যেখানে রসবোধ নাই, সেখানে সাহিত্য
নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আদর্শ দ্বারা সাহিত্যের বিচার হইয়া থাকে। যে
সাহিত্য এক যুগে সচল থাকে, তাহাই পরবর্তী যুগে অচল হইয়া যায়। আবার যাহা এক
যুগে অচল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হয়ত পরবর্তী যুগে সচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এমনও
লেখা আছে, যাহা যুগের আক্রমণ সহ্য করিয়া অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া থাকে। যে-সব
বৈশিষ্ট্যগুণে সাহিত্য যুগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে তাহা যদি তোমার রচনায়
থাকে, তবে তুমি অমর ও কালজয়ী। তুমি কাহাকে আক্রমণ করিয়াছ, কাহার বিরুদ্ধে
লেখনী চালনা করিয়াছ, তাহা দেখিবার বিষয় নহে। সেই আক্রমণের মধ্যে তুমি রসসৃষ্টি
করিতে পারিয়াছ কি না তাহাই দেখিতে হইবে। যদি পার, তবে তোমার রচনা সর্ব্বকালে
সর্ব্বদেশে আদরণীয় ও বরণীয় হইবে। রুশো ও ভল্টেয়ারের কথা ধরা যাক। তাঁহাদের
অনেক লেখা আক্রমণাত্মক। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্ম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
তাঁহারা নিরঙ্কুশ লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের গ্রন্থ কোথাও
আদৃত হয় নাই। প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং তাঁহারা
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিদেশে নির্বাসন-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
ভিক্টর হিউগোকেও নির্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। টমাস পেনকে সমগ্র জীবন অশেষ
নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা ধর্মব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা ও
সমাজব্যবস্থা-কোন কিছুকেই আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহাদের এই সব বিরুদ্ধ
সমালোচনার অনেকগুলি নিতান্ত বাজে ও অযৌক্তিক। কিন্তু তাঁহাদের রচনার মধ্যে
চিরন্তন সত্য ও সাহিত্যের সম্পদ ছিল বলিয়া আজিও তাহা সর্ব্বদেশে আদৃত হইতেছে।
গালাগালি ও আক্রমণ আছে বলিয়া আজ কেহই রুশো, ভল্টেয়ার ইত্যাদিকে অসম্মান করে
না। বরং গত কোন যুগে লোকে তাঁহাদের প্রতি যে অসম্মান দেখাইয়াছিল, আজ আমরা
সমুচিত সম্মান দেখাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। ভাষার
সৌন্দর্য্য, ভাবের গভীরতা, আনন্দের উপাদান, সৃষ্টির বৈচিত্র্য- এই সব থাকিলেই
সাহিত্য অমর হইয়া রহিবে, মানবের চিত্তপটে অপূর্ব্ব প্রভাব আঁকিয়া দিবে। ঠিক এই
ভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যকে আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি নবাব-বাদশাহ্
সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেন ভালভাবে চিত্রিত করেন নাই, তাহা বড়
কথা নয়, তাহা মোটেই ধর্তব্যের বিষয় নহে। তিনি রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন কি না,
কেবল তাহাই দেখিতে হইবে; যদি পারিয়া থাকেন, তবে তিনি প্রত্যেক যুগের
সাহিত্য-রসিকের নিকট চির-আদরণীয়, চির-বরণীয় হইয়া রহিবেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে
মুসলিম-বিদ্বেষ আছে? থাকিলই বা, তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহা অতি সামান্য বিষয়।
রুশো, ভল্টেয়ারকে যেমন আমরা ক্ষমা করিয়াছি, বঙ্কিমকেও সেইরূপ ক্ষমা করিতে
হইবে। কারণ বঙ্কিম-সাহিত্যের চারি দিকে হীরা-জহরৎ এমন ভাবে ছড়াইয়া আছে যে
তাহার প্রলোভনে সামান্য একটু কাদাময়লাকে ভয় করিলে চলিবে না।”২১
সফিয়া খাতুন লিখছেন,
” মরহুম বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসবে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ
করি, প্রণাম করি।
বাংলার সাহিত্যসম্রাট্, “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রের স্রষ্টা, আমাদের জাতীয় জীবনের
প্রথম ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা সাম্প্রদায়িক বলে অপমান করেন, তাঁদের
বুদ্ধির বিকৃতি দেখে মনে ক্ষোভ জাগলেও তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে
একদল মানুষ থাকবেই যারা মূঢ়তা দ্বারা মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে,
মানুষের সত্যকে তারা দেখতে পায় না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে যাঁরা
অস্বীকার করেন, তাঁদের মনোবৃত্তি এত ক্ষুদ্র যে তাতে লজ্জিত হতে হয়।
‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহ’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রভৃতি পুস্তকে যাঁরা
সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু খুঁজে বেড়ান, তাঁদের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।
ইতিহাসের সত্যকে যাঁরা প্রকাশ করেন, কাব্যে বা উপন্যাসে তাঁরা সেই সমসাময়িক
মানুষের মনোভাবকে প্রকাশ করতে বাধ্য। তা না হ’লে সাহিত্যের অঙ্গহানি ঘটে।
সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের বা রাজপুত-পাঠান যুগের পরস্পরের বিরোধী ভাবগুলিকে কাব্যে
বা উপন্যাসে প্রকাশ করলেই লেখককে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া চলে না।
বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে। এবং সেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে ব’লে তিনি
স্পষ্টভাষায় বলেছেন, “হিন্দু হ’লেই ভাল হয় না বা মুসলমান হ’লেই মন্দ হয় না।
আবার মুসলমান হ’লে ভাল হয় না, হিন্দু হ’লে মন্দ হয় না। ভাল মন্দ লোক দুই
সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে।”
সাম্প্রদায়িক মানুষগুলি কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ’তে পারেন নি, তাঁরা এর উপরেও
সুর চড়িয়ে করলেন জাতীয় সঙ্গীত “বন্দে মাতরম্’-এর উপর যুদ্ধঘোষণা। এই সঙ্গীতের
মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করা হয় নি, দেশমাতৃকার স্তব করা হয়েছে।
“মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না- সুজলা, সুফলা,
মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে- জিজ্ঞাসা করিল, ‘মাতা কে?’ উত্তর না করিয়া
ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন- ‘সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
ইত্যাদি।”
মহেন্দ্র বলিল, ‘এ ত দেশ, এ ত মা নয়।’ ভবানন্দ বলিলেন, ‘আমরা অন্য মা মানি না।’
‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।(আনন্দমঠ)
বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিভাকে ছোট ক’রে দেখলে নিজেদেরই ছোট ক’রে দেখা হবে।
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যাঁরা সাম্প্রদায়িক কদর্য্যতাকে সাহিত্য বা ধর্মের
মধ্যে টেনে আনেন, তাঁদের অসাধু উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবার জন্য প্রত্যেক
সত্যাশ্রয়ী মুসলমানের উচিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেখান।
তা যদি আমরা না করি, তা হ’লে জাতীয়তার সঙ্গে সাহিত্যেরও গতি রুদ্ধ হবে।
বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানকে ছোট ক’রে দেখেন নি, তাঁর উপন্যাসে এমন কতকগুলি মুসলমান
চরিত্র আছে, যা নাকি হিন্দু চরিত্র অপেক্ষাও মহৎ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে
বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব মানুষেরই ছবি এঁকেছেন, কাল্পনিক বড় একটা কিছু নাই।
বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার শতবর্ষ পূর্ণ হ’ল। তিনি বাঙালীকে যা দান ক’রে গেছেন,
তা অপূর্ব্ব ও শাশ্বত সুন্দর। আজ বঙ্কিমের শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে বাঙালী
হিন্দু-মুসলমান সমবেত হয়ে আমরা সকলে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।
বন্দে মাতরম্” ২২
উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত গুলি ছাড়াও আরও বহু ব্যক্তিত্বের বিবৃতি থেকে একথা
স্পষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সত্তায় যে আদর্শবাদ, তা মূলতঃ চিত্তশুদ্ধির
জীবনমুখী বিবর্তনে ক্রিয়াশীল। কখনো তা সৌন্দর্যরূপে, কখনো তা শক্তিরূপে, কখনো
তা আধ্যাত্মিকতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সংস্কার ও প্রচলিত নৈতিকতার
বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকেছে। সর্বক্ষেত্রে তার লক্ষ্য হয়েছে নব্য মানবতা,
মুক্তিশীলতা এবং সর্বজনীন কল্যাণ।
পরিশেষে জানাই,বিদ্বেষ এবং ক্ষোভের কোলাহলে বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্প সৌন্দর্য
একদা মুসলমান সমাজের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গিয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টিতে
স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাবার পরে বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই
প্রতিক্রিয়া ক্রমশ প্রশমন লাভ করে, তবে পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় সব সময়ে
বঙ্কিম উপন্যাসকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ হিসেবেই বিবেচনা করে এসেছিলেন।
স্বাধীন বাংলাদেশেও এই মনোভাব একবারে দুর্লভ নয়, একথা দুঃখজনক হলেও সত্য।
তথ্যঋণ:-
১। রতন কুমার নন্দী, মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র,সম্পাদকের কথা।
২। সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্কিমচন্দ্র, শেক বাকের আলি,কথা সাহিত্য,
পৌষ,১৩৯৮,পৃ-৩৭।
৩। ঐ,পৃ-৩৭-৩৮।
৪। কাফেলা, মাঘ, ১৩৮৯,পৃ-২৯-৩৫।
৫।সত্যের সন্ধানে মুসলিম সমাজ,আমিনুল ইসলাম ২০০৬,পৃ-১০১-১৩২ ও বাংলা সাহিত্যে
সাম্প্রদায়িকতা, আমিনুল ইসলাম, ২০০৮,পৃ-৫৬-১০৮।
৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৮।
৭। Historian’s of India, Pakistan and Cylon,T.W. Clerk,edited by C.H.
Philip.
৮। রতন কুমার নন্দী, মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র,সম্পাদকের কথা।
৯। রতন কুমার নন্দী, মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র,সম্পাদকের কথা।
১০। তুহিনা বেগম, “মীর মশাররফ হোসেন: দেশ কালের কথা”, এবং সংস্কৃতি, ২০১৬।
১১। Rames chandra Majumdar, The Renascent India.
১২। উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা’।
১৩। রতন কুমার নন্দী, মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র,সম্পাদকের কথা।
১৪। চন্ডীপ্রসাদ সেন, বাঙালি মুসলমান।
১৫। ‘সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, ২য় খণ্ড।
১৬। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’।
১৭। রতন কুমার নন্দী, মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র,সম্পাদকের কথা।
১৮। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে আকাশবাণী কলকাতা থেকে ১৯৪১
খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন বৃহস্পতিবার, রাত ৯টায় কাজী নজরুল ইসলামের এই কথিকাটি
প্রচারিত হয়।
১৯। সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
২০। বঙ্কিমচন্দ্র, কাজী আব্দুল ওদুদ।
২১। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, রেজাউল করীম।
২২। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সাফিয়া খাতুন,বঙ্কিম-প্রতিভা, সম্পাদনা- বিমলচন্দ্র
সিংহ।
(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)