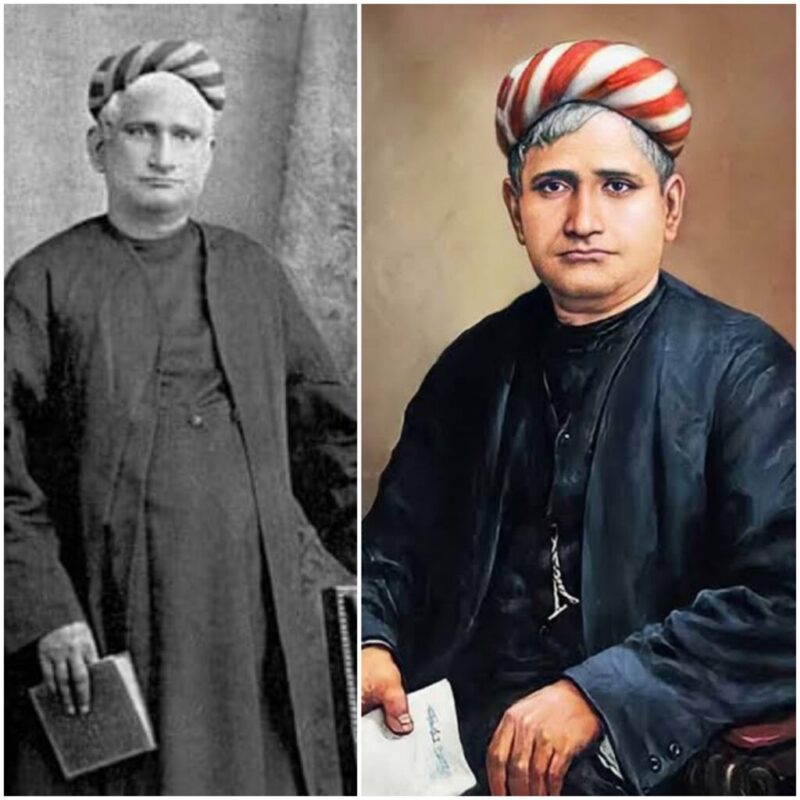বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘আনন্দ মঠ’ একটি যুগান্তকারী উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই উপন্যাসটি কেবল সাহিত্যকর্ম হিসেবেই নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাবের কারণেও এটি এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তবে এই উপন্যাস নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বহু বিদগ্ধ সমালোচক মনে করেন, ‘আনন্দ মঠ’-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ইংরেজ স্তুতি এবং ইংরেজ শাসনকে বিধাতা-নির্দিষ্ট বলে মেনে নেওয়া। তাঁরা এর সমর্থনে উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে হিমালয়বাসী চিকিৎসক ও মঠাধ্যক্ষ সত্যানন্দের কথোপকথনের দিকে ইঙ্গিত করেন। এমনকি কিছু প্রাক্তন বিপ্লবী, যারা পরবর্তীতে মার্কসীয় মতবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের জীবনের এক পর্যায়ে ‘আনন্দ মঠ’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও পরে গ্রন্থটির মূল সুর সম্পর্কে অবহিত হয়ে এটিকে ‘নতুন দর্শন’ দিতে ব্যর্থ একটি গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, এই যুক্তিগুলো একেবারে অস্বীকার করা যায় না, বরং ‘আনন্দ মঠ’-এর বিভিন্ন অংশ থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে এই মতবাদের সমর্থন করা সম্ভব।
তবে, দেশ, কাল, সমাজ, পাত্র এবং পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ‘আনন্দ মঠ’-এর শেষ পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য কিছু অংশের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হবে। গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ইংরেজ-বিদ্বেষ, স্বাদেশিকতা এবং রক্তক্ষরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বানই হলো ‘আনন্দ মঠ’-এর মূল বাণী।
‘আনন্দ মঠ’ প্রকাশ ও রাজরোষের সূত্রপাত:-
‘আনন্দ মঠ’ ধারাবাহিকভাবে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র (এপ্রিল, ১৮৮১) সংখ্যা থেকে ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ (মে, ১৮৮২) সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এরপর ১২৮৯ বঙ্গাব্দেই (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২) এটি পুস্তকাকারে প্রথম সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয়। সে সময় বহু ইংরেজ কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তেন এবং ‘বঙ্গদর্শন’-এর প্রতিটি সংখ্যাই সরকারি দপ্তরে জমা পড়তো। ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত ‘আনন্দ মঠ’-এর বিভিন্ন কিস্তি পাঠ করে সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। এর প্রমাণ মেলে তাঁর সরকারি চাকরিতে।
১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর অর্থ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্রনাথ মিত্র অবসর গ্রহণ করলে বঙ্কিমচন্দ্র অস্থায়ীভাবে সেই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েক মাস বাদেই, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি, মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করা হয়। এরপর তাঁকে আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে লিখেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে “গোপন তথ্যাদি প্রকাশ” করার অভিযোগটি ছিল নিছকই “বাজে দোষারোপ”। পত্রিকাটি ইঙ্গিত দেয় যে, কয়েকজন সেক্রেটারি একজন ভারতীয়কে পুনরায় এই পদে নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁরাই এই অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।
অন্যদিকে, ইংরেজ রবার্ট নাইট সম্পাদিত পত্রিকা ‘স্টেটসম্যান’ (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২) জানায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই এবং তাঁর বদলি তাঁর চরিত্র বা কর্মদক্ষতার ওপর কোনো কটাক্ষপাত নয়। ‘স্টেটসম্যান’ যেহেতু সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও জানান যে মেকলে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের সুখ্যাতি করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টে লিখেছিলেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ তুলে দিয়ে ‘আন্ডার-
সেক্রেটারি’ পদ সৃষ্টি করা হয়, যা কেবল ইংরেজদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ‘বঙ্গদর্শন’-এ ‘আনন্দ মঠ’ প্রকাশের সময় ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সব বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, যা ইংরেজ কর্মচারীদের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং এর ফলস্বরূপই তাঁকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ থেকে অপসারণ করা হয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ইংরেজ বিদ্বেষ:-
‘আনন্দ মঠ’ প্রকাশকালে ‘বঙ্গদর্শন’-এর প্রকাশ খুব অনিয়মিত ছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা (আগস্ট ১৮৮১) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে। এই সংখ্যাতেই প্রথম ইংরেজ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন: “আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেস্টিংসও বিকম্পিত হইলেন”। বিদ্রোহী সন্তানদের দমনের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন টমাসকে পাঠানো হলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যর্থতাকে হাস্যকরভাবে তুলে ধরেন: “কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল”।
দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্যাপ্টেন টমাসের মিথ্যা জয়ের রিপোর্ট এবং তাঁর নির্লজ্জ চরিত্র তুলে ধরা হয়। তিনি “জনকতক চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী, বুনো” লুটেরাদের বন্দি করে কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান যে “১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে”। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে স্পষ্ট করে দেন যে “কেবল শেষ কথাটিই সত্য” অর্থাৎ কেবলমাত্র ৭ জন বন্দী হয়েছিল। এরপর ক্যাপ্টেন টমাসের চরিত্রকে আরও নীচে নামিয়ে আনা হয় যখন তিনি সাঁওতাল কুমারীদের “গুণগ্রহণে মনোযোগ” দেন এবং জীবানন্দ-পত্নী শান্তিকে তাঁর “উপপত্নী” হওয়ার পরামর্শ দেন। শান্তি তাঁকে “রূপী বাঁদর” বলে অভিহিত করেন। ভবানন্দের মতে ইংরেজরা হলো “অসুরের বংশ”।
এই ধরনের শ্লেষাত্মক মন্তব্য এবং ইংরেজদের নৈতিকতার প্রতি এই ধরনের কটাক্ষ সহ্য করতে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ১৮৮২ সালের ১৬ জানুয়ারি ‘বঙ্গদর্শন’-এর শ্রাবণ সংখ্যা সরকারি দপ্তরে জমা পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ২২ জানুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদায়ের নোটিশ দেওয়া হয়। বাংলা সরকার তাঁকে আর তাঁদের দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা নিরাপদ মনে করেনি। আদালতে মামলা করার মতো যথেষ্ট তথ্য না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্রকে পরোক্ষভাবে শাস্তি দিয়ে ‘সরকারের অসন্তোষ’ বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
চাকরির জীবনে অস্থিরতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা:-
এই রাজরোষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা তাঁর একটি পত্রে (৪ বৈশাখ ১২৮৯ / ১৬ এপ্রিল ১৮৮২) তিনি লেখেন: “ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিকপালগণ পূর্বমত দিক্ পালন করিতেছেন। চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হলেই আনন্দমঠ বজায় হয়।” এই পত্রে তাঁর মানসিক অস্থিরতা এবং সরকারি চাপের প্রতি তাঁর সচেতনতা স্পষ্ট।
তাঁর বদলির ধরনও তাঁর ওপর সরকারের বিরূপতার ইঙ্গিত দেয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারিতে আলিপুরে বদলি, ৪ মে বারাসতে, ১৭ মে আবার আলিপুর, অতঃপর ৮ আগস্ট উড়িষ্যার জাজপুর। এই ঘন ঘন বদলি তাঁর জন্য অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ছিল, যা কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা তাঁর অপর একটি পত্রে (৬/১/৮৩) ফুটে উঠেছে। তিনি লেখেন: “আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে।…. সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ, আত্মোদর-পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, ‘বন্দে উদরং’।…. আপনিও ‘শাপেনাস্তংগমিত মহিমা,’ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই এদশাপ্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়; কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণী সৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল “যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরিণী নদী” সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উড়িষ্যার বৈতরিণী পারেই যমদ্বার বটে।” এই পত্রগুলি তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তাঁর চারপাশে স্বদেশী শত্রুতার ইঙ্গিত দেয়।
১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আবার হাওড়ায় বদলি করা হয়। এরপর ১৮৮৫-র ১ জুলাই ঝিনাইদহ, ‘৮৬-র ১৭ মে উড়িষ্যার ভদ্রক, ১০ জুলাই আবার হাওড়া, ‘৮৭-র ১৯ মে মেদিনীপুর এবং সবশেষ ‘৮৮-র ১৬ এপ্রিল তিনি আলিপুরে আসেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর অবসরগ্রহণ পর্যন্ত তিনি আলিপুরেই ছিলেন। এই তেত্রিশ বছরে তিনি প্রায় চব্বিশবার বদলি হয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি বলেছিলেন, “চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ।” ‘আনন্দ মঠ’ রচনার পর সরকারি কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন সত্যিই বিষময় হয়ে উঠেছিল।
সরকারি মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মদক্ষতা:-
‘আনন্দ মঠ’ রচনার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাই পেয়ে এসেছেন। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ১৮৭৭-৭৮ সালের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রকে “অতীব ক্ষিপ্র, বুদ্ধিমান, মানসিক দিক দিয়ে রীতিমত উৎসাহী, উচ্চশিক্ষার অধিকারী এবং কাজের ব্যাপারে একেবারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন” একজন অফিসার হিসেবে বর্ণনা করেন। কমিশনারও এই মন্তব্য সমর্থন করে যোগ করেন যে, তিনি “একজন উচ্চ চরিত্রের মানুষ, খুবই কর্মঠ এবং খুব ভালোভাবেই কাজ করেন।” ১৮৭৯-৮০ এবং ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টগুলিতেও তাঁর কর্মদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল।
তবে, ‘বঙ্গদর্শন’-এ ‘আনন্দ মঠ’ প্রকাশিত হওয়ার পর হঠাৎ তাঁর সম্পর্কে সরকারি ধারণার পরিবর্তন হয়। তিনি ‘অকেজো’ ও ‘অপদার্থ’ হয়ে উঠলেন। বই প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিরূপতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-৮২ সালের রিপোর্টে বলা হয় যে, তিনি “একজন দক্ষ কর্মী, কিন্তু অতি বাগাড়ম্বরপ্রিয়, অগোছানো ও সারবত্তাহীন।” ১৮৮৩-৮৪ সালে হাওড়ার কালেক্টর বলেন যে, “তাঁর কাজকর্ম নির্দিষ্ট মানে রাখতে গেলে তাঁর প্রতি সর্বদা নজর দিতে হবে।” এরপরের বছরগুলোতেও তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য আসে, যেমন “বিচারকার্য ভালভাবে করছেন না”, “কাজে একেবারেই মন নেই”, “বাগবহুল… অস্বাভাবিক মতপোষণকারী।”
সরকারি চাকরিতে তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং ক্রমাগত বদলি তাঁকে হতাশ করে তোলে। সম্ভবত এইসব কারণেই ১৮৯১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে, সরকার তাঁর অবসর গ্রহণের আবেদন মেনে নেয়। মজার বিষয় হলো, ১৮৯০-৯১-এর প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে সরকারের সুর পরিবর্তন হয়। জেলা শাসক তাঁকে “একজন অতি দক্ষ, সৎ ও নির্ভরযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট” হিসেবে বর্ণনা করেন এবং তাঁর অবসর গ্রহণকে “একটা দুর্ভাগ্য বিশেষ” বলে মনে করেন। এই পরিবর্তন স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে সরকারের মনোভাব বদলাচ্ছিল।
রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি: এক রাজনৈতিক কৌশল?:-
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কেন এই সরকার বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘রায়বাহাদুর’ এবং ‘সি. আই. ই.’ উপাধি দিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই কোনো উপাধির জন্য লালায়িত ছিলেন না। ‘রজনী’ উপন্যাসে অমরনাথের উক্তি, “রাজ দরবারের মান-সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি”, তাঁর মানসিকতা স্পষ্ট করে। তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক রচনা ‘ইংরাজ স্তোত্র’ও স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানান যে তিনি নিজে কখনোই এই সব উপাধির প্রার্থী হন নি, এমনকি ‘গেজেটে’ উপাধির তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।
তাঁর একদা বিরোধী হাওড়ার কালেক্টর মিঃ বাক্ল্যাণ্ড, যিনি পরবর্তীকালে তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী হয়েছিলেন, তিনি লিখছেন যে, “রাজ সরকারে চাকরি করা অপেক্ষা বিদ্বৎমণ্ডলীতে তাঁর খ্যাতির জন্য তাঁকে খেতাবগুলি দেওয়া হয়।” এই মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। দেশবাসীর হৃদয়রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তখন ‘স্বদেশবৎসল’ কৃতী ও যশস্বী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। নরমপন্থী নিয়ন্ত্রিত জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলি দেশে তখন এক জাগরণের সৃষ্টি করেছে এবং চরমপন্থীদের উত্থানও ঘটছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসকে হাতে রাখার জন্য সরকার ১৮৯২ সালে নতুন এক আইন (Indian Council Act, 1892) পাশ করে দেশবাসীকে ছিটে-ফোঁটা শাসন সংস্কার উপহার দিল। সম্ভবত দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘রায়বাহাদুর’ এবং ‘সি.আই. ই.’ উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে ‘সাহিত্য-সম্রাট’-কে লেখেন: “আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে।”
রাজরোষ এড়ানোর কৌশল: ‘আনন্দ মঠ’-এর পরিবর্তন:-
‘আনন্দ মঠ’ রচনার পর রাজরোষ থেকে বাঁচবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী কৌশল অবলম্বন করেন? শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন যে তিনি “অনেক বিবেচনার পর আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।” ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত ‘আনন্দ মঠ’ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ‘আনন্দ মঠ’-এর বিভিন্ন সংস্করণ লক্ষ্য করলেই তাঁর কৌশল ধরা পড়বে। উপন্যাসের গুণ বৃদ্ধি নয়, কেবলমাত্র রাজরোষ থেকে বাঁচার তাগিদেই বিভিন্ন সংস্করণে তিনি নানা ধরনের পরিবর্তন করেছিলেন। এই পরিবর্তনগুলো ছিল ইংরেজের পক্ষে নিন্দনীয় বহু অংশ বর্জন এবং স্তুতিবাচক বহু কথার সংযোজন।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল উপক্রমণিকা অংশে। ‘বঙ্গদর্শন’-এ যেখানে ছিল “পণ আমার জীবন সর্বস্ব” এবং প্রতিশব্দ “এ পণে হইবে না” এবং “তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব”, সেখানে প্রথম সংস্করণে এল “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।” এবং “ভক্তি”। ‘ভক্তি’ কথাটি মোটা অক্ষরে লেখা ছিল – অর্থাৎ দেশমাতৃকার জন্য জীবনদানের পরিবর্তে তাঁর উদ্দেশে ভক্তি অর্পণ করাই কাম্য। ‘উৎসর্গ পত্র’-তেও শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভক্তিযোগাধ্যায় থেকে শ্লোক এবং ‘কুমারসম্ভব’ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তি আরোপের কথা বলা হলো। এই সংযোজনের ফলে গ্রন্থের মূল লক্ষ্য রাজনীতি থেকে ধর্মে পরিবর্তিত হয়।
এছাড়াও, গ্রন্থের সূচনায় তিনি ‘বিজ্ঞাপন’ নামে এক নতুন বিষয়ের অবতারণা করলেন। প্রথম সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপনে’ তিনি লিখলেন: “ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।” তিনি বিদ্রোহীদের “আত্মঘাতী” বললেন। কিন্তু একই সাথে, গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদে শান্তি ও জীবানন্দের বিদায়ে লেখক গভীর দুঃখ প্রকাশ করে লিখছেন: “হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?” অরাজকতা সৃষ্টিকারী আত্মঘাতী বিপ্লবীদের জন্য এত হাহাকার কেন – এই প্রশ্নটি এখানে থেকেই যায়।
গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় একাদশ পরিচ্ছেদে সন্তান দলের সঙ্গে ইংরেজ ও ফৌজদারি সৈন্যের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। ‘বঙ্গদর্শনে’ (১২৮৮ আশ্বিন, পৃঃ ২৫৪-২৫৫) সর্বত্রই ছিল ‘ইংরেজ’ বা ‘ইংরেজ সেনা’। প্রথম সংস্করণে সেখানে হলো ‘যবন’ ‘যবন সেনা’, বা ‘নেড়ে’। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ছিল “সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত ইংরেজসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল।” সেখানে প্রথম সংস্করণে ‘ইংরেজসেনা’ পরিবর্তিত হয়ে ‘যবনসেনা’ হয়। মুষ্টিমেয় সন্তানদলের হাতে ৫০/৬০ জন ইংরেজ সেনাকে হত্যার কথা প্রথম সংস্করণে “২০/৩০ জন গোরা সৈন্য” করে দেওয়া হয়, যা ভারতীয়দের হাতে ইংরেজ নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। একইভাবে, জীবানন্দের “ঐ যে দেখিতেছ লাল কাল জরদা সবুজ, ও পাঁচরঙা মুগের লাডু, উহাতে ফৌজদারী বাদসাহী ইংরেজী আছে, চল ভাই বৈষ্ণব সেবায় সব লাগাই” – এই ধরনের উক্তি প্রথম সংস্করণে বাদ গেল।
এই ধরনের নানা পরিবর্তনের পরেও সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি সম্পর্কিত গোপন রিপোর্ট এবং তাঁর বদলির বহর তা স্পষ্ট করে।
কেশবচন্দ্র সেন ও ‘লিবারেল’ পত্রিকার সমালোচনা:-
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন যে, এ সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রকে জানান যে, ‘আনন্দ মঠ’-এর জন্য তিনি বিপদে পড়বেন। তবে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ‘আনন্দ মঠ’-এ রাজদ্রোহমূলক কিছু নেই, তবেই তিনি মুক্তি পেতে পারেন। ওই ইংরেজই পরামর্শ দিলেন যে, ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে ভালো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারলে বিপদের কোন আশঙ্কা থাকবে না। কেশবচন্দ্র সেন সরকারি মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।
এমতাবস্থায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী কেশবচন্দ্রের পরামর্শে তৎভ্রাতা জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁরই সম্পাদিত ‘দি লিবারেল এ্যান্ড দি নিউ ডিসপেনসেশন’ পত্রিকায় ৮ এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ‘আনন্দ মঠ’-এর সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই সমালোচনার তারিখটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই ভুলটি চলে আসছে যে সমালোচনাটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ভুলটি সাহিত্য পরিষৎ এবং সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলিতেও বিদ্যমান।
১২৯০ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে) চুঁচুড়া থেকে মুদ্রিত হয়ে ‘আনন্দ মঠ’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাতেই সর্বপ্রথম ‘দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন’ শিরোনামায় ‘লিবারেল’ পত্রিকার সমালোচনার কিছু অংশ যুক্ত হয়। সেখানে সালের জায়গায় ছাপার ভুলে ১৮৮৩ হয়ে যায় ১৮৮২। এই ভুলের প্রতি সর্বপ্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁর সমালোচনায় মন্তব্য করেন যে, স্বৈরাচারী মুসলিম শাসনকে ধ্বংস করে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনে সাহায্য করাই হলো ‘আনন্দ মঠ’-এর সন্তানদলের লক্ষ্য। তিনি লেখেন: “দেশে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হওয়াটা কি সত্যই কোন দৈবপ্রেরিত বিষয়? অথবা প্রশ্নটাকে আরও চূড়ান্তভাবে উপস্থাপিত করে বলা যায় কী উদ্দেশ্যে, কোন্ বিশেষ কর্মের তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এই দেশে ব্রিটিশকে পাঠালেন? গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ঈশ্বরের সেই তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে-মুসলিম স্বৈরাচার ও বাংলাদেশের অরাজকতার অবসান ঘটানোই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে এই উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।” তিনি আরও লেখেন যে, গ্রন্থকারের মতে, “পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে জাতীয় জীবনে সকল সত্যের বিকাশ সাধনের জন্য তা প্রয়োগ করতে ভারত বাধ্য।”
কৃষ্ণবিহারী সেনের এই মতামত উদ্ধৃত করার আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন: “প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকা স্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।” এই ‘বিজ্ঞ সমালোচক’ যে কৃষ্ণবিহারী সেন, তার প্রমাণ কৃষ্ণবিহারীর বংশধরদের একটি মুদ্রিত পুস্তকে মেলে, যেখানে লেখা আছে: “আনন্দমঠ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গভর্নমেন্টের বিরাগভজন হন, পরে কৃষ্ণবিহারী উহার ভূমিকা লিখিয়া দেওয়াতে গভর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হয়।”
কেবলমাত্র ‘বিজ্ঞ সমালোচক’-এর মতামত যুক্ত করা নয়, গ্রন্থের অভ্যন্তরেও বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সেই একই – রাজরোষ প্রশমন করা। মহাপুরুষ কথিত তত্ত্বকথার সঙ্গে তিনি যোগ করেন: “ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে-নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।” দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বে যেখানে ছিল “ব্রত সফল হইবে না-কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?” তার পরিবর্তে এল নতুন কথা: “ব্রত সফল হইয়াছে-মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ-ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।” এরপর মহাপুরুষের উক্তি: “শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।” এই ধরনের ইংরেজ স্তুতি নিশ্চয়ই অকারণে নয় এবং এতে ‘আনন্দ মঠ’-এর মূল সুরের ছন্দপতন ঘটলো।
এছাড়াও, “বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল”র পরেও যে অংশটি ছিল – “বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব” – দ্বিতীয় সংস্করণে এই কথাগুলি বাদ গেল। “পারি ত সে কথা পরে বলিব” কি কথা? নিশ্চয়ই তা প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্র অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু ‘আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে’, তাই তিনি তা পারেননি। ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে নিন্দনীয় উক্তিগুলিও এই সংস্করণে তিনি বাদ দিলেন। উদাহরণস্বরূপ, “ক্যাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কন্টক হইয়। সাঁওতাল কুমারীদিগের গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন” স্থলে এল “দ্রৌপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।” ‘বঙ্গদর্শন’ ও প্রথম সংস্করণে যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়াটসনকে ব্যঙ্গ করে একজন সন্তান যে উক্তি করছিল, তা সমেত পুরো পরিচ্ছেদের অনেকটাই বাদ গেল। সন্তানদের “দস্যু না দেবতা?” – এই প্রশংসামূলক প্রশ্নটি পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে হলো “এরা কি রকম দস্যু?”
সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আড়ালে আশ্রয়:-
এত চেষ্টার পরেও কিন্তু বিশেষ কোনো সুফল ফলল না। ‘আনন্দ মঠ’ যে রাজদ্রোহমূলক নয়, ইংরেজ তা মানতে নারাজ। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ফড়কের সঙ্গেও এ কাহিনির যথেষ্ট মিল আছে। ফড়কের কার্যকলাপ সরকারের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে এবার কাহিনির পটভূমিকা বোঝাতে বিশেষ তৎপর হতে হয় এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সে পটভূমিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। তিনি লিখছেন যে, ফড়কের জীবন-কাহিনিই হলো ‘আনন্দ মঠ’-এর পটভূমিকা এবং কেবলমাত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আড়ালে আশ্রয় নেন। তিনি লিখছেন যে, দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত কোথাও তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেননি। “কৃষ্ণবিহারী সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনার পটভূমি নিশ্চয়ই খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ সমালোচনায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উল্লেখ নেই-অর্থাৎ তখনো বঙ্কিম সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আড়ালে আশ্রয় নেবার কথা ভাবেন নি।”
তবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতবাদের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও বলা যায়, ‘আনন্দ মঠ’-এর পটভূমিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহই ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রেরণা হলো হান্টারের ‘Annals of Rural Bengal’ এবং ম্যাৎসিনির জীবনচরিত। সন্ন্যাসীদের দেশপ্রেমের সঙ্গে ফড়কের কোনো সম্পর্ক নেই। অধ্যক্ষ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তৎকালীন ইতিহাস নিশ্চয়ই তাঁর অজানা ছিল না। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা অন্য কিছু নয়, কৃষ্ণবিহারী সেনের উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, সন্তানদলের বিদ্রোহ ছিল অপদার্থ মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে, এবং ইংরেজ তাঁদের মিত্র। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামটি ইতিপূর্বে উচ্চারিত হয়নি ঠিকই, তবে যে-ব্যক্তি হান্টারের বইয়ের নানা অংশ এবং পরিশিষ্ট থেকে দুর্ভিক্ষ ও সমকালীন রাজনীতির বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, তিনি কি তা হলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কিত আলোচনাটি বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাঁচার তাগিদে উক্ত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করেন? তা নয়, ব্যাপারটি তিনি প্রথমে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবস্থা জটিলতর হলে বাঁচার জন্য তাঁকে ‘আনন্দ মঠ’-এর পটভূমিকাটির কথা জানাতে হয়। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে ‘আনন্দ মঠ’-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে ‘দেবী চৌধুরাণী’ প্রকাশিত হয়। ‘দেবী চৌধুরাণী’-র বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন: “এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।” “এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া” কথাটি লক্ষণীয়।
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন যে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বঙ্কিম-সুহৃদ চন্দ্রনাথ বসু ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই সরকারের কাছে ‘আনন্দ মঠ’ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। যে রিপোর্টটি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর দেওয়া উচিত ছিল, তা দেওয়া হলো দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর। চন্দ্রনাথ বসু জানান যে, ‘আনন্দ মঠ’-এর প্রেরণা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন: “দেবী চৌধুরাণীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম গ্রেইগ ও হান্টারের বিবরণ উল্লেখ করেন নি। অথচ চন্দ্রনাথের রিপোর্টে এদের উল্লেখ আছে। তিনি কোথা থেকে পেলেন এই খবর? নিশ্চয়ই দুজনে আলোচনা করে একটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে রিপোর্টে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এমন অনুমান করা অসঙ্গত না।” চিত্তরঞ্জনবাবু ঠিকই বলেছেন – দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তাঁর রচনার উৎস সম্পর্কে জানিয়েছিলেন এবং রাজরোষ প্রশমনের জন্য এটা সরকারকে জানাবার দরকার ছিল। বঙ্কিম-সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তো স্পষ্টই বলছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দ মঠ’-এর পটভূমিকা সম্পর্কে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথাই বলেছেন। চন্দ্রনাথ তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, ‘আনন্দ মঠ’-এর সন্তানেরা হান্টারের সন্ন্যাসীবেশী দস্যু নয় – “তাঁরা হলেন উচ্চ সংস্কৃতিবান ও আত্মত্যাগী মানুষ, যাঁরা স্বৈরাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন চিন্তাশীল মস্তিষ্ক, এবং প্রেমপূর্ণ ও বিশ্বাসপরায়ণ হৃদয়ের অধিকারী খাঁটি মানুষ।”
কৃষ্ণবিহারী সেন ‘লিবারেল’ পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ধর্মের আসনে বসিয়েছেন। এতে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যা করে লেখেন – গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে দেশহিতৈষণার দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত, কিন্তু গ্রন্থকারের দেশপ্রেম শান্তি ও সুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে-সমস্ত বাঙালি লেখক দেশের স্থায়ী স্বার্থ এবং বর্তমান শাসনের মঙ্গলময় দিকটিকে মানতে চান না, তাঁদের মতো বর্তমান গ্রন্থকারের দেশপ্রেম অজ্ঞাতপ্রসূত, বিবেচনাহীন ও বিপজ্জনক নয়।
‘আনন্দ মঠ’-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণের পরিশিষ্টে তিনি প্লেইগ (Gleig)-এর Memoirs of the Life of Warren Hastings এবং হান্টারের Annals of Rural Bengal-এর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিচয় দিলেন। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন: “এবার পরিশিষ্টে বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল। আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গলায় হইয়াছিল। আর Captain Edwards নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না-কেন না, উপন্যাস-উপন্যাস, ইতিহাস নহে।” আসলে বঙ্কিম জানাতে চাইছেন যে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনিই তিনি ‘আনন্দ মঠ’-এ বর্ণনা করেছেন – এ জন্যই তাঁর এত প্রয়াস।
গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাস্থল বীরভূম নয় বলে শুধু উল্লেখই করলেন, মাত্র গ্রন্থমধ্যে কোন পরিবর্তন করলেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে: উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বীরভূমকে কেন ঘটনাস্থল বলে বেছে নিয়েছিলেন? এখানেও সেই রাজরোষের আশঙ্কা। ‘বঙ্গদর্শন’-এ (১২৮৭, চৈত্র, পৃ, ৫৮০) প্রকাশিত প্রথম খণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে তিনি লিখছেন যে, ইংরেজ তখন সারা বাংলাদেশের দেওয়ান। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য, কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার ওপর। কর সংগ্রহের জন্য বীরভূমে তখনও কোনো ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হয়নি। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করে কলকাতায় পাঠাতেন। সাধারণ মানুষ মনে করত যে বীরভূমের শাসক মুসলিম রাজা – ইংরেজ নয়। সন্তানদের যুদ্ধ মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে, ইংরেজের বিরুদ্ধে নয় – এটা দেখাবার জন্যই বীরভূমের আমদানি হয়। তৃতীয় সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপনে’ বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করলেন যে, ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গ – বীরভূম নয়। এছাড়া, এই সংস্করণে ওয়ারেন হেস্টিংসের চিঠিপত্র ও ডেসপ্যাচ থেকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি পরিশিষ্ট যোগ করলেন। গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে ‘বীরভূম’ স্থলে এল ‘বাঙ্গালা’, বীরভূমের রাজধানী ‘রাজনগর’ স্থলে এল ‘নগর’ (১/৭), ‘অজয়ের জলে’ স্থলে ‘নদীর জলে’ (১/১৮ ও ৩/৮), কেন্দুবিল্ল গ্রামে ‘গোস্বামীর মেলা’ স্থলে এল ‘নদীতীরে একটি মেলা’ (৪/৪)। এধরনের নানা পরিবর্তন করে তিনি বীরভূম নাম ঘোচাতে চাইলেন, কিন্তু এতেও সর্বত্র এ পরিবর্তন করা সম্ভব’ হয় নি – বরেন্দ্রভূমির ছাপ সর্বত্রই রয়ে গেছে। ‘বঙ্গদর্শন’ ও ‘আনন্দ মঠ’-এর প্রথম তিনটি সংস্করণের তৃতীয় খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ পঙ্ক্তিতে ছিল – “এরূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সন্তান নাম কীর্ত্তিত করিতে লাগিল।” চতুর্থ সংস্করণ থেকে এটি বাদ গেল। এরই বা কারণ কি? বঙ্কিম দেখাচ্ছেন সন্তানদলের যুদ্ধ মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে, কিন্তু ১১৮০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলার ওপরেই তো কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – কোম্পানি তখন আর দেওয়ান নয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর শাসনকালেই টমাস (৩১ ডিসেম্বর ১৭৭২) এবং এডওয়ার্ডস (১ মার্চ, ১৭৭৩) বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের এই সব সাধারণ বিষয়গুলি নিশ্চয়ই জানতেন। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা সে যুগে লেখা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি বেছে নেন মুসলিম শাসিত বীরভূমকে। এসবই বাঁচার জন্য প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন যে, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ১৭৭২-৭৩ সালেই শেষ হয়ে যায় নি – অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত তাদের হাঙ্গামা চলেছিল, কিন্তু রাজরোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বঙ্কিমকে সে কাহিনি শেষ করতে হয় অন্যভাবে।
চতুর্থ সংস্করণে তিনি কয়েকটি স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়ে ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করেন। প্রথম তিনটি সংস্করণে (১।১০) ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছে – “আমাদের রাজা রক্ষা করে কই?” পরে রাজার স্থানে এল “মুসলমান রাজা।” এই সংস্করণের শেষ অধ্যায়ে মহাপুরুষ-কথিত তত্ত্বকথা অংশে ‘সত্যানন্দ কাতর হইও না”-র পরে যুক্ত হলো – “তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।” মহাপুরুষ-কথিত তত্ত্বকথার সঙ্গে এই কথাটি যোগ হওয়ায় নিশ্চয়ই তত্ত্বকথার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।
গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণেও (১৮৯২) তিনি বেশ কিছু পরিবর্তন করেন এবং ‘বিজ্ঞাপনে’ সে কথা জানিয়ে দেন। এইসব পরিবর্তনে কাজ হয়েছিল এবং সরকার ‘আনন্দ মঠ’ বাজেয়াপ্ত করেন নি – বরং ১৮৯২ ও ১৮৯৪-এ তিনি যথাক্রমে ‘রায় বাহাদুর’ ও ‘সি. আই. ই’ উপাধিতে ভূষিত হচ্ছেন। ১৯১৭ সালে জেম্স ক্যাম্পবেল কার (James Campbell Ker) সম্পাদিত ভারতীয় বিপ্লববাদের গোপন দলিল ‘Political Trouble In India 1907-17’ গ্রন্থে বলা হচ্ছে – “আনন্দ মঠ হলো ১৭৭২-১৭৭৪ সালের তথাকথিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনি।… বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থগুলিতে এমন অনেক অংশ আছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে লেখক ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্থায়ী সরকারের মঙ্গলময় দিক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।” ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পদস্থ সরকারি কর্মচারী Sir Verney Lovett রচিত ‘A History of the Indian Nationalist Movement’ গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, ‘আনন্দ মঠ’-এর সন্তানদলের বিদ্রোহ স্বৈরাচারী মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে – ইংরেজ তাঁদের মিত্র। ১৯২৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Earl of Ronaldshay রচিত ‘The Heart of Aryavarta’ গ্রন্থেও লেখক একই কথার প্রতিধ্বনি করে লিখছেন – “গ্রন্থের মূল বক্তব্য হলো হিন্দুধর্মের শত্রুদের উচ্ছেদ সাধন করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটানো। গ্রন্থে বর্ণিত সময়ের সেই শত্রু হলো মুসলিম শাসন।”
পরবর্তীকালে বঙ্কিম-সুহৃদ রমেশচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস. ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’তে লেখেন যে, ‘আনন্দ মঠ’-এ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং সম্মিলিত মুসলমান ও ইংরেজ সেনাদলের ওপর সন্ন্যাসীদের বিজয়ের কাহিনি বিবৃত হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ এক রহস্যময় মহাপুরুষের আবির্ভাবে কোনো হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, কারণ এই মহাপুরুষ সত্যানন্দকে জানান যে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য অন্তত কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন আছে। এই গ্রন্থের মূল শিক্ষা হলো এই যে, স্বৈরাচারী মুসলিম শাসনের একমাত্র বিকল্প ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ শাসন। বঙ্কিমচন্দ্র ফড়কের কাহিনি রচনা করে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করতে চান নি – সন্ন্যাসী বিদ্রোহই যে তাঁর রচনার উৎস এটাই তিনি সরকারকে জানাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন – এবং ইংরেজ বিরোধিতার পরিবর্তে স্বৈরাচারী মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
বঙ্কিমচন্দ্র কি ইংরেজ শাসনের সমর্থক?:-
এবার ফিরে যাওয়া যাক মূল প্রসঙ্গে – ইংরেজ-স্তুতিই কি ‘আনন্দ মঠ’-এর প্রতিপাদ্য বিষয়, সত্যিই কি ‘আনন্দ মঠ’-এ বঙ্কিমচন্দ্র নতুন কোনো ‘দর্শন’ দিতে পারেন নি – যার অভাবে একদল মুক্তিকামী মানুষ নতুন পথে পা বাড়ালেন? সুপ্রকাশ রায় ‘আনন্দমঠে’ বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার শিক্ষা না দিয়ে ইংরেজ প্রভুদের সহিত সহযোগিতা করার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি ‘আনন্দমঠ’কে হিন্দু “রিনাসান্স” এবং ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পক্ষে প্রচারের সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু “রিনাসান্স” বা ‘নবহিন্দুবাদ’ ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিকূল। সুপ্রকাশ রায় আরও অভিযোগ করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’-এ “বিরাট গণ-অভ্যুত্থানকে পাশ কাটাইয়া গিয়া এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।” তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগ্রাম হিসেবে ‘সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের’ ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইংরেজ শাসনের গুণগান গেয়েছেন।
ভারত ইতিহাস, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্ক সুপরিচিত কোনো ব্যক্তি যদি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এ ধরনের মতামত প্রকাশ করেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্যের সততা এবং দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগে। বলাবাহুল্য, কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই নন – রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এবং ভারতের তাবৎ শ্রদ্ধেয় মনীষী ও জাতীয়তাবাদীগণ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করে উক্ত গবেষক তাঁর একদেশদর্শিতা, ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত, অস্বচ্ছ ও বিকৃত ধারণার পরিচয় দিয়েছেন এবং ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ইতিহাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকাটুকুই নিয়েছিলেন – সন্ন্যাসীদের চরিত্র, ভাবাদর্শ, কর্মোদ্যম এবং ‘আনন্দ মঠ’-এর ভাবধারা সবই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। সন্তানদলের ‘মহাব্রত’ ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এদিক থেকে সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিকৃত ব্যাখা করেছেন। তাদের ব্যর্থ বিদ্রোহ সফল হলে দস্যু ও লুঠেরাদের হাতে বাংলার ইতিহাসে যে ‘স্বর্ণযুগের’ অভ্যুদয় হত, শ্রীসুপ্রকাশ রায় নিশ্চয়ই তাকে বিধাতার চরমতম অভিশাপ বলেই আখ্যায়িত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেন নি বা মুসলিম বিদ্বেষও প্রচার করেন নি – ভারত ইতিহাস ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাই তা মেনে নেবেন। এছাড়া, মুসলিম সম্প্রদায়ও তখন ‘ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত’ ছিল না। ওয়াহাবি বিদ্রোহ, ফরাজি বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহের কাল তখন শেষ হয়েছে। ভারতের বুকে তখন মুসলিম রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আলিগড় থেকে – যার প্রধান লক্ষ্যই হলো ইংরেজ তোষণ এবং হিন্দু বিরোধিতা, কংগ্রেস বিরোধিতা, বাঙালি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রচার।
আসলে উনিশ শতকের বাঙালি মানসে একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নবাবী শাসনের রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার স্মৃতি, ইংরেজ শাসনে পরাধীনতার গ্লানিবোধ, আবার অপরদিকে ইংরেজ শাসনের কল্যাণকর দিক প্রভৃতি নানা দ্বন্দ্বে সেদিন বাঙালি চিত্ত দোলায়িত। তাই বাঙালি সমাজ একদিকে সিপাহি বিদ্রোহের নিন্দায় মুখর, আবার অপরদিকে লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতীয়া তোপির বীরত্বে স্ফীতবক্ষ। ইংরেজের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে একদিকে প্রবল আগ্রহ, অপরদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ। ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যের কবি তাই একই সঙ্গে সিরাজের পরাজয়ে মর্মাহত এবং ক্লাইভের প্রতি প্রশংসাবাক্যে সমান তৎপর। বস্তুত ইংরেজের প্রভাবে সেদিন বাঙালি সমাজ এক ‘সম্মোহন শক্তি’ দ্বারা অভিভূত হয়েছিল।
বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন (১৯২২-২৩ সালে) “ইংরাজ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে আমাদিগকে অদ্ভুত সম্মোহন মন্ত্রের দ্বারা মূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল।” এই সম্মোহন শক্তির ফলেই ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে – জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি শতধা বিভক্ত ভারতে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, জাতি প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের পরমোপকারী বঙ্কিমচন্দ্র তা স্বীকার করেছেন। ইংরেজ ভারতবাসীকে অনেক নতুন জিনিস শিখিয়েছে এবং তার মধ্যে প্রধান হলো স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা (‘ভারত কলঙ্ক)। যতদিন না দেশ স্বশাসনের উপযুক্ত হয় ততদিন পরের সুশাসন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় – সে ইংরেজ বা মুসলমান যাই হোক না কেন। প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ থাকা সত্ত্বেও ‘আনন্দ মঠ’-এর সন্তানদল দস্যুবৃত্তির দ্বারা রণে জয়ী হয়েছিল, মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ ছিল তাদের অন্তর। এই সংকীর্ণতা বঙ্কিমচন্দ্র মানতে পারেন নি। তিনি চান প্রকৃত পরিশীলিত মানুষ – তাঁদের নেতৃত্বেই দেশে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। মহৎ কাজের জন্য চাই প্রকৃত অনুশীলন। ‘সন্তান দল’ অনুশীলিত নয় – তাঁদের মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম, ভক্তি ও কর্মের প্রকৃত সমন্বয় হয় নি, তাঁরা লুঠেরা ও মুসলিম বিদ্বেষী ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারেন নি, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করতে পারেন নি, ভবানন্দ ও জীবানন্দ ব্রতভঙ্গকারী জেনেও দল-নায়ক সত্যানন্দ কেবলমাত্র রণজয়ের তাগিদে তাঁদের আত্মহত্যা থেকে বিরত করেছেন। এ সবই তো ‘আত্মঘাতী’ কর্ম ও আত্মপ্রবঞ্চনা। অনুশীলনের অভাবে ‘আনন্দ মঠ’-এর ‘সন্তান দলের’ দেশপ্রেম কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজে পায় নি – তাঁরা ব্যর্থ হলেন। এরপর ‘দেবী চৌধুরাণী’-কে তিনি দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে পরিশীলিত করতে চাইলেন, কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা। ধরলেন ‘সীতারাম’-ফল একই। সেখানেও ব্যর্থতা এল। সারা উনিশ শতক ধরে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা জাতীয় জীবনে একজন নায়কের অনুসন্ধান করেছেন। কেউ দধীচি, ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, শিবাজি, প্রতাপাদিত্য বা রাণা প্রতাপের মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই নায়ক হলেন শ্রীকৃষ্ণ – পূর্ণ অনুশীলিত মানুষ। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ তুল্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান তিনি করেছিলেন সত্যানন্দ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রমুখের মধ্যে। অবশেষে ইতিহাসের ‘রাজসিংহের’ মধ্যে সে মানুষ মিলল। যোগ্য নায়ক, যোগ্য আধার ব্যতীত সর্ব প্রয়াস যে ব্যর্থ হবেই তার প্রমাণ মিলল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ত্রয়ী’-তে।
‘আনন্দ মঠ’-এ দস্যুবৃত্তির দ্বারা রণজয় হলো – প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই এল বিসর্জন, স্বৈরাচারী মুসলিম শাসন ধ্বংস হলো, কিন্তু হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো না। দেশের রাষ্ট্রশক্তি কার হাতে যাবে? দেশে তখনও তো কোনো সমাজ নেই – যে সমাজ ছিল তা মৃত। প্রজাশক্তি জেগে ওঠেনি – জেগে উঠেছে মুষ্টিমেয় ‘সন্তানদল’। তাঁরা তো সমাজ নন – সংঘমাত্র। তাঁদের হাতে শাসনভার পড়লে দেশে নিশ্চয়ই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত না – বরং তাঁদের উচ্ছেদের জন্য নতুন আরেকটি বিদ্রোহের প্রয়োজন হত এবং ভারতে মধ্যযুগের স্থায়িত্ব আরও দীর্ঘায়ত হত। সুতরাং ‘সাহিত্য-সম্রাট’ ইংরেজের হাতে দেশের শাসনভার দিলেন – তাদের শাসনাধীন বহির্বিষয়ক জ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে দেশে গড়ে উঠল মধ্যবিত্ত সমাজ – যে সমাজ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। রামমোহনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও চেয়েছিলেন, কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসন। ইংরেজ শাসনাধীনে স্বাধীনতার উপযুক্ত হওয়ার পর স্বাধীনতা অর্জনের দাবি করতে হবে। জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে দেশের বহু বিপ্লবী নেতার কণ্ঠেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। ‘ভারতের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, শাসনকর্তা ভিন্ন জাতীয় হলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হয় না বা শাসন কর্তা স্বজাতীয় হলেই রাজ্য স্বাধীন হয় না। আবার ‘ভারত কলঙ্ক’ প্রবন্ধে বলছেন – স্বজাতীয় বা বিজাতীয় – যাই হোক না কেন, সুশাসন করলে দুই রাজাই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করবে, আর পরজাতীয় রাজা সুশাসন করবে না, এর কেনো স্থিরতা নেই। সমগ্র ভারত ইতিহাসের দিকে তাকালে এ উক্তির যথার্থতা মিলবে। স্বাধীনতার দু’টি দিক আছে – বহিঃস্বাধীনতা ও অন্তঃস্বাধীনতা। মুষ্টিমেয় অর্বাচীনের হাতে দেশের শাসনভার পড়লে দুই ধরনের স্বাধীনতাই যাবে – অন্তঃস্বাধীনতা যাবে সবার আগে।
বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে বাঙালি ও ইংরেজের মধ্যে একটা বৈরীভাব জেগে থাকুক। ‘জাতিবৈর’ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন যে, জাতিবৈরতা থাকলেই প্রতিযোগিতা থাকবে। ইংরেজের কাছে অপমানিত হলেই ভারতবাসী তাঁদের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করবে। তাঁর মতে, উন্নত শত্রু উন্নতির সহায়ক এবং উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। তিনি লিখছেন – “বাঙালী ইংরেজদের প্রতি বিরক্ত থাকুক, … ইংরেজ বাঙালীর প্রতি বিরক্ত থাকুক,” কিন্তু কেউ যেন কারো অনিষ্ট কামনা না করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন – বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যতক্ষণ বিদেশি প্রভুশক্তির সঙ্গে সন্ধি ও সোলেনামার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ মারাত্মক বিদ্রোহের পথ অবলম্বন অধর্ম। এই সন্ধি ও সোলেনামার দিকে সর্বদাই তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল এবং এজন্যই দেশবাসীকে তিনি নিজেদের বাহুবল, ধনবল ও বিদ্যাবল সংগ্রহ করার জন্য প্রণোদিত করেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মতে, বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতিতে সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য সংগ্রাম নয়, সন্ধির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা।
বঙ্কিম-শিষ্য সাহিত্যিক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় লিখছেন যে, তৎকালে বঙ্কিম ইংরেজের সঙ্গে বিবাদে না গিয়ে দেশবাসীকে ইংরেজের সমতুল্য হতে বলেছিলেন। তিনি লিখছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন – “আত্মোৎসর্গ শিক্ষা কর, কিন্তু যতদিন সাহেবদিগের সমকক্ষ না হও, সাহেবদিগের সহিত বিবাদ করিও না। যখন ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, তখনকার আনন্দমঠ’ তখনকার গ্রন্থকার রচনা করিবেন।” সত্যিই তাই – বিশ শতকের সূচনায় নতুন যে যুগ এল, তাতে রচিত হলো নতুন ‘আনন্দ মঠ’ – অরবিন্দ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অগ্নিময়ী নিবেদিতা, বারীন ঘোষ নতুন ‘আনন্দ মঠ’ রচনায় ব্রতী হলেন। ‘স্বরাজ,’ ‘যুগান্তর’ ‘বন্দে মাতরম্,’ ‘সন্ধ্যা’, ‘কর্মযোগীন’-এ সেদিন সরাসরি বিদ্রোহ আর বিপ্লবের ডাক দেওয়া হলো – সমগ্র ভারতভূমিই সেদিন পরিণত হলো ‘আনন্দ মঠ’-এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সেদিন ‘আনন্দ মঠ’-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলো। এত ভাবসম্পদের পরেও ‘আনন্দ মঠ’-এ কেউ যদি কোন ‘দর্শনের সন্ধান’ না পান তবে তা ‘আনন্দ মঠ’-এর দোষ নয় – সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিই এর সঙ্গে জড়িত।
কোনো স্বাধীন দেশের সাহিত্যিককে ‘আনন্দ মঠ’ রচনা করতে হয় না – পরাধীন দেশে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নানা গোঁজামিল দিয়ে জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচিত হয় – এর মধ্যে কিছু গ্রন্থ থাকে, যাদের আবেদন চিরন্তন। ‘আনন্দ মঠ’-ও সেই শ্রেণির গ্রন্থ। রাজরোষ থেকে বাঁচার জন্য নানা পরিবর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটিকে ইংরেজ শাসকদের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন, কিন্তু তাতেও গ্রন্থটির মূল সুর বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ‘আনন্দ মঠ’ প্রেরণা দেবে, ভারতের ঘরে ঘরে আজও ‘আনন্দ মঠ’ সাড়া তোলে, চিরদিন তুলবে এবং পরাধীন জাতিকে যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদের শেকল ছিঁড়তে অনুপ্রাণিত করবে।
গ্রন্থ-পঞ্জী:-
————-
১। ‘একটি উপন্যাস এবং একজন রাজকর্মচারী’, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৮৮-৯৬, এবং আনন্দ মঠঃ উৎস সন্ধানে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃঃ
২। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৩১৮, পৃঃ ১৭৩-৭৪।
গ্রন্থাকা
৩। ঐ, পৃঃ ১৭৪-৭৬।
৪। ঐ। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত ‘বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম’ গ্রন্থে (তৃতীয় সংস্করণ, মজিলপুর, ২৪-পরগণা, পৃঃ ১০-১১) ভিন্ন প্রকার বিবরণ দিয়েছেন।
৫। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সরকারি মতামতের জন্য Character Book of the Subordi-nate Executive Service, Part II (MSS.), Bengal Past and Present, V. 90. 1971-এ Dr. N. K. Sinha-র প্রবন্ধ Bankim Chandra Chatterjee in the Little World of a Civil Servant; সে যুগের রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যব্রত তপাদার, ১৯৮৫ দ্রষ্টব্য।
৬। কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১৯৮৯, পৃঃ ২৫।
৭। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এ তথ্যের কোন সূত্র নির্দেশ করেন নি।
৮। Militant Nationalism in India, B. B. Majumdar, 1966, P.187.
৯। আনন্দ মঠঃ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৮-৩৯।
১০। Liberal পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ‘আনন্দমঠ’ (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ), অথবা ‘আনন্দ মঠ’: রচনার প্রেরণা ও পরিণাম, পৃঃ ৮৫-৮৬ দ্রষ্টব্য।
১১। ‘একটি উপন্যাস এবং একজন রাজকর্মচারী, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৯০।
১২। বঙ্কিম গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ গ্রন্থে (১৯৮১) জানাচ্ছেন যে, এ সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান “সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্ম কেশব সেনের পৌত্রের কাছে শুনে আমাকে বলেছেন।”-পৃঃ ১৩৪।
১৩। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ‘আনন্দ মঠ’: রচনার প্রেরণা ও পরিণাম’ গ্রন্থের পৃঃ ৩৯।
১৪। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত, প্রথম নবপত্র সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ১২১।
১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৯৪।
১৬। ঐ পৃঃ ১৯৫।
১৭। বঙ্গদর্শন, ১৩১৯, ভাদ্র সংখ্যা, পৃঃ ৩১৭।
১৮। চন্দ্রনাথ বসুর রিপোর্ট-টির জন্য: আনন্দ মঠঃ উৎস সন্ধানে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃঃ ১০৩-০৪ দ্রষ্টব্য।
১৯। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য: বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে, ভবতোষ দত্ত, ২০০৯, পৃঃ ২৮-২৯ এবং Militant Nationalism in India, B. B. Majumdar, 1966, P. 196-97 দ্রষ্টব্য।
২০। Political Trouble in India 1907-1917, James Campbell Ker, বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, Calcutta, 1973, P. 29-30.
২১। A History of the Indian Nationalist Movement, Sir Verney Lovett, London, 1968, P. 281-82.
২২। The Heart of Aryavarta, Earl of Ronaldshay, London, 1925, P. 114.
২৩। দ্রঃ আনন্দমঠ, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
২৪। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, সুপ্রকাশ রায়, ১৯৭২, পৃঃ ১৭১-৭৪।
২৫। পরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।
২৬। বঙ্কিম সরণী, প্রমথনাথ বিশী, ১৩৮৪, পৃঃ ১৭৪-৭৫।
২৭। ঐ, পৃঃ ৭।
২৮। নবযুগের বাংলা, বিপিন চন্দ্র পাল, ১৩৭৯, পৃঃ ২৪৯-৫০।
২৯। বঙ্গদর্শন, ১৩১৩, আষাঢ়, পৃঃ ১০১।
৩০।আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, জীবন মুখোপাধ্যায়।
(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)